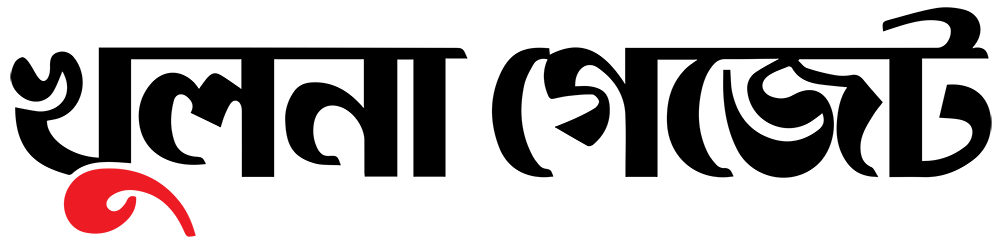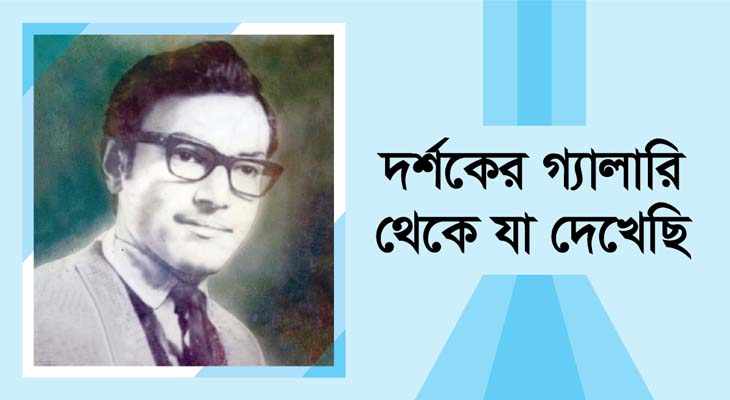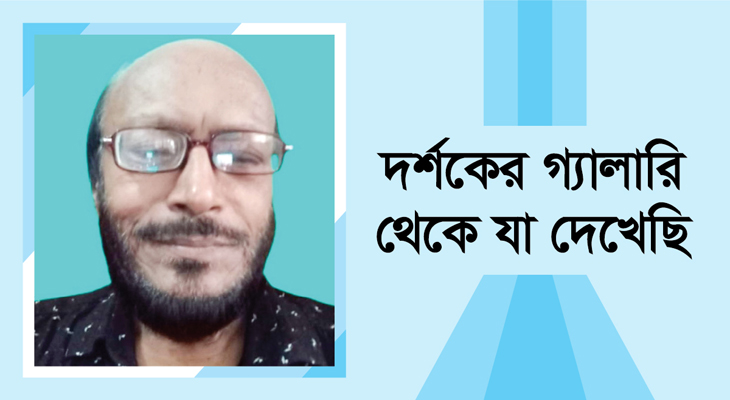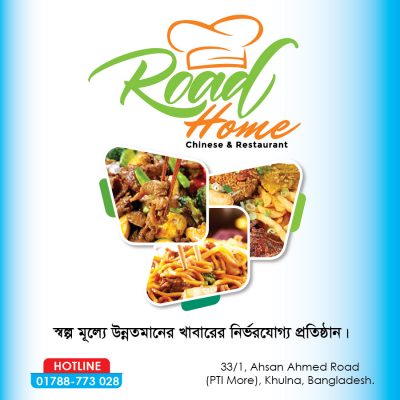১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ফসল পাকিস্তানের স্বাধীনতা, ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট। স্বাধীনতা পরবর্তী বিষাদময় সংঘাতের সূচনা হয় তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে। কেবলমাত্র অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রাধান্য পায়নি, রাষ্ট্রভাষা নিয়েও বিরোধের কারণ হয়। পাকিস্তানের স্বাধীনতার আগের মাসে ৪৭ সালের জুলাইতে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ডঃ জিয়াউদ্দিন আহম্মদ উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করেন। জ্ঞান তাপস খ্যাতিমান ভাষাবিদ ডঃ মুহম্মদ শহিদুল্লাহ যুক্তি দেখান ‘যদি বিদেশী ভাষা বলে ইংরেজি ভাষা পরিত্যক্ত হয় তবে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ না করার কোন যুক্তি নাই’।
করাচীতে অনুষ্ঠিত সরকারী শিক্ষা সম্মেলনে পাকিস্তানের শিক্ষা মন্ত্রী ফজলুর রহমানের সমর্থনে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বা ‘লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা’ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর প্রতিবাদে ৪৭ সালের ৬ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে এক মিছিল বের হয়। মিছিল পূর্ব সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পাকিস্তান তমুদ্দুন মজলিসের সম্পাদক আবুল কাশেম। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতিদানের আশ্বাস দেন। তৎকালীন পাকিস্তানের গণ পরিষদের সদস্য ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি গণ পরিষদে উর্দু এবং ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে ঘোষণার দাবি তোলেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নবাবজাদা লিয়াকাত আলী খান এ দাবি তোলার জন্য গণ পরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্র নাথ দত্তকে অসৌজন্যমূলক ভাষায় আক্রমণ করেন।
পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে সমর্থন করেন। ১৯৪৮ সালের ১৫ মার্চ মুখ্যমন্ত্রী রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের সাথে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। মুখ্যমন্ত্রী অঙ্গীকার করেন ‘বাংলাকে প্রদেশের রাষ্ট্রভাষা করা হবে’। দেশের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দেন। তৎকালীন ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার নিজেদের শ্রেণি স্বার্থে এ চুক্তির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান শাসনতন্ত্রের মূলনীতি নির্ধারক কমিটির রিপোর্টে সুপারিশ করেন উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের চুক্তিকে দুর্বলতার নামান্তর, ভারতীয় কমিউনিস্টদের কাছে আত্মসমর্পণ বলে অভিহিত করেন। এ সময় আন্দোলন এত তীব্র হয় যে, ছাত্ররাই ১৯৪৯ সালে মুসলিম লীগ বিরোধী রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা নেয়। অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও অবক্ষয়ের কারণে মুসলিম লীগের একাংশ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়ায়। একই সাথে এগিয়ে আসে পাকিস্তান অবজারভার, দৈনিক ইনসাফ ও দি মেইল নামক পেশোয়ারের দৈনিক।
পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত সাড়ে ৪ কোটি বাঙালি দ্ব্যর্থহীন কন্ঠে দাবি তোলেন বাংলাকে উর্দুর পাশাপাশি রাষ্ট্র ভাষা ও জাতীয় ভাষার মর্যাদা দিতে হবে। ইতোমধ্যে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রকট হতে থাকে। ১৯৪৮ সালের ২৭ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। একই বছর ২১ মার্চ ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে ও ২৪ মার্চ কার্জন হলে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন ‘টৎফঁ ধহফ ড়হষু ঁৎফঁ ংযধষষ নব ঃযব ংঃধঃব ষধহমঁধমব ড়ভ চধশরংঃধহ’। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাৎক্ষণিক এর প্রতিবাদ করেন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক সত্যযুগ পত্রিকায় ঢাবি’র ছাত্রদের প্রতিবাদের ওপর ভিত্তি করে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সত্যযুগ নামক এই পত্রিকাটি খুলনায় আসার পর তৎকালীন দৌলতপুর বিএল একাডেমীর শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।
ভাষা আন্দোলন মূলতঃ দু’পর্বে বিভক্ত। আট চল্লিশকে বলা হয় ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্ব আর বায়ান্ন চূড়ান্ত পর্ব। ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাঙালি জাতির সফল ও স্বার্থক আন্দোলন। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে স্বোচ্চার ছাত্রদের প্রতি জনসমর্থন বাড়তে থাকে। ১৯৫১ সালের ১১ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে পাকিস্তান গণ পরিষদের সদস্যদের কাছে রাষ্ট্রভাষা বাংলা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করা হয়। ঐ স্মারকলিপি পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক মহলকে খুব একটা স্পর্শ না করলেও সাংবাদিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ডন পত্রিকার পরোক্ষ সমর্থনের পাশাপাশি পেশোয়ারের খাইবার মেইল পত্রিকা সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ‘বাংলা ভাষার দাবি অবহেলা করা যায় না, আমরা মনে করি বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাকে পাকিস্তানী সরকারী ভাষা রূপে স্বীকার করা উচিৎ’। ১৯৫১ সাল জুড়ে ভাষা বিষয়ক তৎপরতা ছিল লক্ষ্য করার মত, যা একুশের বিস্ফোরক পটভূমি তৈরীতে সাহায্য করে। রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে গড়ে ওঠা অনুকূল পটভূমি সত্ত্বেও সরকারের তৎপরতা বন্ধ থাকেনি। সরকার ও মুসলিম লীগ সমর্থকরা তখনও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র করে। ভাষা সংগ্রামী আহমদ রফিক রচিত ভাষা আন্দোলন নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ১৯৫১ সালের ১৫ এপ্রিল পাকিস্তানে উর্দু সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে মাওলানা আকরাম খাঁ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মতামত প্রকাশ করেন। এ বক্তব্যের প্রতিবাদে তৎকালীন পাকিস্তান অবজারভার বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৮ এপ্রিল এ পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয় ‘মাওলানা আকরাম খাঁ উর্দু সম্মেলনে বলেন যে, যারা উর্দুর বিরোধিতা করবে তারা ইসলামের শত্রু’। ১৯৫১ সালে বাংলা ভাষার পক্ষে জনমত গড়ে ওঠে, যা ভবিষ্যৎ আন্দোলনের জন্য মজবুত ভীত তৈরি করে। এ সব তৎপরতা ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিকে বাঙালির জীবনে এক তাৎপর্যময় সময় হিসেবে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।
পটভূমি হিসেবে আরও নানা দিক থেকে সময়টা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্ববঙ্গের মানুষ তখন খাদ্য সংকট, লবণ সংকট, পাটের বাজার মন্দাসহ নানা সমস্যায় জর্জরিত। চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী আন্দোলন, ভূখা মিছিল, অর্থনৈতিক মন্দা এবং সেই সঙ্গে সরকারী দমন নীতি, নির্যাতন সবকিছু মিলেই একুশের পটভূমি তৈরি করে। দেশব্যাপী অসন্তোষের প্রেক্ষাপটে গণবিস্ফোরণ ঘটাতে একটা ইস্যুর প্রয়োজন ছিল। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিনের ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারির ভাষণ সেই ইস্যু সৃষ্টি করে।
ভাষা আন্দোলনে খুলনাঞ্চলের মানুষের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। সে সময় এত রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠন না থাকলেও সচেতনতা ও মূল্যবোধ থেকে এখানকার বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আন্দোলনে ভূমিকা নেয়।
১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের দিকে দৌলতপুর বিএল একাডেমীর ছাত্র সংসদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ছিলেন এ কে চাঁন মিয়া (স্বাধীনতা পরবর্তীতে পুলিশ সুপার) ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শেখ হাসান উদ্দিন (পরবর্তীতে তথ্য কর্মকর্তা)।
পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ’র এই উক্তির পর খুলনা বিএল একাডেমীতে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, ছাত্র কংগ্রেস ও ছাত্র ফেডারেশন ঐক্যবদ্ধ হয়। গড়ে ওঠে ভাষার দাবিতে ছাত্র আন্দোলন।
আট চল্লিশের পঁচিশ ফেব্রুয়ারি। পাকিস্তানের করাচী আইন সভায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি ওঠে। কুমিল্লার গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত এ দাবি তোলেন। তিনি কংগ্রেস এর আদর্শ ও দর্শনে বিশ্বাসী। তার স্বোচ্চার কণ্ঠের দাবি ইথারে এসে পৌঁছায় দৌলতপুর বিএল কলেজে। বাঙালি চেতনা বোধ থেকে সমবেত কণ্ঠে ছাত্ররা স্লোগান দেয় “রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই”। পূর্ব পাকিস্তান মুসিলম ছাত্রলীগ, ছাত্র কংগ্রেস ও ছাত্র ফেডারেশন নিজেদের মতাদর্শ ভুলে ভাষার দাবিতে এক কাতারে সমবেত হয়। আটচল্লিশ-এর ছাব্বিশ ফেব্রুয়ারি বিএল কলেজে বাংলা ভাষার আন্দোলন শুরু হয়। সে সময়কার ছাত্রলীগ নেতা, ভাষা সৈনিক তাহমিদ উদ্দীনের লেখা থেকে এ তথ্য পাওয়া যায়। কুমিল্লার গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের দাবি প্রত্যাখ্যান হওয়ার পর ১৯৪৮ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি বিক্ষুব্ধ ছাত্র সমাজ দৌলতপুর বিএল একাডেমীতে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। মুসলিম ছাত্রলীগ নেতা আব্দুল হামিদ সভায় সভাপতিত্ব করেন। বক্তৃতা করেন তমদ্দুন মজলিসের এস এম আমজাদ হোসেন, সাতক্ষীরার মুনসুর আলী, জগদীশ বসু প্রমুখ। বক্তারা খাজা নাজিমুদ্দিনের বক্তব্যের নিন্দা এবং ধীরেন্দ্র নাথ দত্তের বক্তব্যকে সাধুবাদ জানান (অ্যাডর্ণ পাবলিকেশন-এর মহান একুশে সুবর্ণ জয়ন্তী গ্রন্থ)।
১৯৪৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি বিএল একাডেমীতে ছাত্র সমাজ বিক্ষোভ মিছিল এবং প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে।
আটচল্লিশ-এর ২৯ ফেব্রুয়ারি দৈনিক আজাদে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয় ২৮ ফেব্রুয়ারি খুলনা, দিনাজপুর, পাবনা ও মুন্সীগঞ্জে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। খুলনার দৌলতপুরে আয়োজিত প্রতিবাদে সমাবেশের গৃহীত প্রস্তাবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানানো হয়। একই বছরের ২৬ ফেব্রুয়ারি উল্লিখিত তিনটি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে বিএল কলেজে গড়ে ওঠে ভাষা সংগ্রাম পরিষদ (স ম বাবর আলী রচিত মহান একুশে স্মরণিকা-২০১৫)।
কমিটির আহবায়ক মুসলিম ছাত্রলীগ নেতা তাহমিদ উদ্দীন, সদস্যবৃন্দ- মুসলিম ছাত্রলীগ নেতা ও সাবেক ভিপি এ কে চাঁন মিয়া (পরবর্তীতে পুলিশ সুপার), ছাত্র কংগ্রেস ও কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি ড. শৈলেষ চন্দ্র ঘোষ, ছাত্র ফেডারেশনের সরদার আনোয়ার হোসেন, ধনঞ্জয় দাস, সন্তোষ দাশ গুপ্ত, স্বদেশ বোস, ছাত্রলীগের জিল্লুর রহমান, এম নূরুল ইসলাম (পরবর্তীতে বিএনপি’র সংসদ সদস্য), খোন্দকার আব্দুল হাফিজ (পরবর্তীতে সংসদ সদস্য), এস এম এ জলিল (ফুটবল খেলোয়াড়), কাজী মোঃ মাহাবুবুর রহমান (পরবর্তীতে আইনজীবী), শেখ রাজ্জাক আলী (পরবর্তীতে স্পিকার), এম মনসুর আলী (পরবর্তীতে বস্ত্রমন্ত্রী), এস এম আমজাদ হোসেন (পরবর্তীতে শিক্ষামন্ত্রী), শেখ হাসান উদ্দিন, এম ডি মোমিন উদ্দীন আহমেদ (পরবর্তীতে শিক্ষামন্ত্রী), যুব মুসলিম লীগ নেতা আবু মুহম্মদ ফেরদৌস, আফিল উদ্দীন ও মতিউর রহমান।
বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে গড়ে ওঠা সংগ্রাম পরিষদ আটচল্লিশের ১১ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের ১৭ জেলায় হরতাল আহ্বান করে (সিরাজ উদ্দীন আহমেদ রচিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান)।
১৯৪৮ সালের ১০ মার্চ ঃ সরকারের পরামর্শে খুলনায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন স্তব্দ করার জন্য ১০ মার্চ তৎকালীন পুলিশ সুপার মহিউদ্দিন আহমেদ আন্দোলনরত ছাত্র নেতৃবৃন্দকে নিয়ে বৈঠকে বসেন। বৈঠকে পুলিশ সুপার ছাত্র নেতৃবৃন্দের কাছে যুক্তি তুলে ধরেন এ আন্দোলন মূলত পাকিস্তানকে দুই ভাগ করার জন্য। আর এর পেছনে রয়েছে হিন্দু ও কমিউনিস্টরা। বৈঠকে ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে তাহমিদ উদ্দিন আহমেদ, জিল্লুর রহমান, এস এম আমজাদ হোসেন, মোমিন উদ্দিন আহমেদ, আফিল উদ্দিন ও আবু মুহাম্মদ ফেরদাউস উপস্থিত ছিলেন। (বাসুদেব বিশ্বাস বাবলা রচিত খুলনা জেলার ভাষা আন্দোলন ও ভাষা সৈনিক) ছাত্র নেতৃবৃন্দ পুলিশ সুপারের পরামর্শ উপেক্ষা করে ১১মার্চ খুলনায় সর্বত্র ধর্মঘট সফল করার আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েন।
স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার জন্য ১৯৪৮ সালের ১০ মার্চ অপপ্রচার চালায় ছাত্রনেতা তাহমিদ উদ্দিন আহমেদ, শৈলেন ঘোষ, স্বদেশ ঘোষ, সন্তোষ গুপ্ত ও ধনজয় দাসকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। মূলত এটা ছিল গুজব (অ্যাডার্ণ পাবলিকেশন এর মহান একুশে সুবর্ণ জয়ন্তী গ্রন্থ)
১০ মার্চ মিউনিসিপ্যাল পার্কে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে ছাত্র সমাজ এক জনসভার আয়োজন করে। জনসভায় এ কে চাঁন মিয়া, শেখ রাজ্জাক আলী, মোমিন উদ্দিন আহমেদ, মুনসুর আলী, খন্দকার আব্দুল হাফিজ, কাজী মাহবুবুর রহমান, শৈলেন ঘোষ, সন্তোষ দাস গুপ্ত, এস এম এ জলীল, শেখ কামাল উদ্দিন, সৈয়দ কামাল বকস সাকী, শেখ কামাল উদ্দিন, আবুল কালাম শামসুদ্দিন সুনু মিয়া ও এম এ বারী বক্তৃতা করেন।
১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ঃ খুলনায় খান-এ-সবুর বৃটিশ আমল থেকেই প্রভাবশালী নেতা। ছাত্র ধর্মঘট সফল করার জন্য মুসলিম ছাত্রলীগ, ছাত্র কংগ্রেস ও ছাত্র ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ খান-এ-সবুরের স্মরনাপন্ন হয়। তিনি প্রথমে ভাষা আন্দোলনকে সমর্থন করলে ইস্তেহারে তার নাম ছাপা হয়। ইস্তেহার জিলা স্কুল, মডেল স্কুল, সেন্ট যোসেফস স্কুলে বিলি করা হয়। ছাত্র নেতা আব্দুল রউফের নেতৃত্বে পোষ্টার লেখা ও সাঁটানো হয়। খান-এ-সবুর পরবর্তীতে ইস্তেহার থেকে তার নাম প্রত্যাহার করেন। ১০ মার্চ পুলিশ সুপারের সাথে ছাত্র নেতৃবৃন্দের বৈঠকে পুলিশ সুপার ছাত্র নেতৃবৃন্দকে অবহিত করেন ইস্তেহার থেকে খান-এ-সবুর নাম প্রত্যাহার করেছেন। বৈঠক শেষে ছাত্র নেতৃবৃন্দ খান-এ-সবুরের বাসভবনে (আজকের খুলনা প্রেসক্লাব) গেলে জানতে পারেন তিনি ঢাকার উদ্দেশ্যে খুলনা ত্যাগ করেন।
১১ মার্চ ধর্মঘট সফল, জনমত গঠন এবং ছাত্র সমাজকে সংগঠিত করার জন্য মুসলিম ছাত্রলীগ, ছাত্র কংগ্রেস ও ছাত্র ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ বিএল কলেজে বসে সিদ্ধান্ত নেন সভা, সমাবেশ, মিছিল ও পোস্টারিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তুলে বিএল কলেজ ভাষা সংগ্রাম কমিটি একটি ইস্তেহার ছাপায়। ১১ মার্চ খুলনা শহরে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। বিএল কলেজ ও স্থানীয় মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা মিছিল বের করে। বিএ কলেজ, মহসিন হাইস্কুল, মডেল হাইস্কুল, সেন্ট যোসেফস হাইস্কুলে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। সন্ধ্যায় স্থানীয় গান্ধী পার্কে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন ছাত্র ফেডারেশন নেতা আনোয়ার হোসেন। সন্ধ্যায় পুলিশ তাকে ও স্বদেশ বসুকে গ্রেফতার করে। ১৯২৬ সাল থেকে ১৯৪৮ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বঙ্কু বিহারী ভট্টাচার্য্য অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৮ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৫২ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
১৯৪৮ সালের ১৩ মার্চ : পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে বিএল একাডেমী, আর কে কলেজসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের ১৭ জেলার ন্যায় খুলনাতে ১৪ ও ১৫ মার্চ হরতাল পালিত হয়।
১৯৪৮ সালের ২৫ মার্চ : ঢাকার অনুকরণে বিএল একাডেমীতে ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্লাশ বর্জন করে। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নার উক্তির প্রতিবাদে ২৫ মার্চ সকাল ১০টায় কলেজ গেটে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। নেতৃত্বে ছিলেন ছাত্র ফেডারেশনের স্বদেশ বসু, সন্তোষ দাস গুপ্ত, আনোয়ার হোসেন, মুসলীম ছাত্রলীগের তাহমিদ উদ্দিন আহমেদ, জিল্লুর রহমান, মতিয়ার রহমান ও ছাত্র কংগ্রেসের শৈলেন ঘোষ। জিলা স্কুলের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী ধনঞ্জয় দাস, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হন। তিনি ছাত্র ফেডারেশনের দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। পরবর্তীতে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন। ঐ দিন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের কয়েকজন সংগঠক শাটেল ট্রেন যোগে বিএল একাডেমীতে পৌছে আন্দোলনের সাথে একাতœতা ঘোষনা করেন। সমাবেশে মুসলিম ছাত্রলীগের তাহমিদ উদ্দিন আহমেদ, ছাত্র সংসদের ভিপি এ কে চাঁন মিয়া, ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক শেখ হাসান উদ্দিন, কাজী মাহবুবুর রহমান (পরবর্তীতে এ্যাডভোকেট), তমদ্দুন মজলিশের এস এম আমজাদ হোসেন (পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষামন্ত্রী), মোমিন উদ্দিন আহমেদ (পরবর্তীতে জাপা সরকারের শিক্ষামন্ত্রী, শেখ রাজ্জাক আলী (বিএনপি সরকারের আমলে স্পিকার), এম মুনসুর আলী (বিএনপি সরকারের বস্ত্রমন্ত্রী), ফুটবল খেলোয়াড় এস এম এ জলিল, যুব নেতা আবু মোহাম্মদ ফেরদৌস, আফিল উদ্দিন আহমেদ, আবুল কালাম আজাদ (পরবর্তীতে অধ্যক্ষ), এম. নুরুল ইসলাম (নগর বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি), নড়াইলের খন্দকার আব্দুল হাফিজ (পরবর্তীতে সংসদ সদস্য), মেহেরপুরের জিল্লুর রহমান (পরবর্তীতে সংসদ সদস্য), গোলাম সরোয়ার, আইনুল হক, সৈয়দ মোশাররফ হোসেন, আব্দুল করিম, এনামুল হক, ছাত্র কংগ্রেসের শৈলেন ঘোষ, ছাত্র ফেডারেশনের সন্তোষ দাস গুপ্ত, স্বদেশ ঘোষ ও আনোয়ার হোসেন বক্তৃতা করেন।
১৯৪৮ সালের ২৬ মার্চ ঃ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে খুলনা রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে তিনটি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত ভাষা সংগ্রাম পরিষদ এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। মিছিলটি নীলা সিনেমা হল (আজকের পিকচার প্যালেস), লোয়ার যশোর রোড, বাবুখান রোড ও আহসান আহমেদ রোড দিয়ে মিউনিসিপ্যাল পার্কে এসে সমবেত হয়। পুলিশের বাধার মুখে পার্কের দক্ষিণ গেটে সংক্ষিপ্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে সভার সিদ্ধান্তবলী পাঠ ও সরকার বিরোধী নানা স্লোগান উচ্চারিত হয়। সরকার বিরোধী স্লোগানের অপরাধে পুলিশ ছাত্রনেতা তাহমিদ উদ্দিন আহমেদ, জিল্লুর রহমান, খন্দকার আব্দুল হাফিজ, স্বদেশ বোস, সন্তোষ দাস গুপ্ত ও আনোয়ার হোসেনকে গ্রেফতার করে। পরে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়।
১৯৪৮ সালে স্বদেশ বসু গ্রেফতার হন। ৭ বছর কারা ভোগ করার পর ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে মুক্তি লাভ করেন। ১৯৪৯ সালে ঢাকা জেলে থাকাকালীন ৫৮দিনের অনশন ধর্মঘটে অংশ নেন। খুলনায় ভাষা আন্দোলনে প্রথম গ্রেফতার মতিয়ার রহমান, মানোষ দাস গুপ্ত ও স্বদেশ বসু।