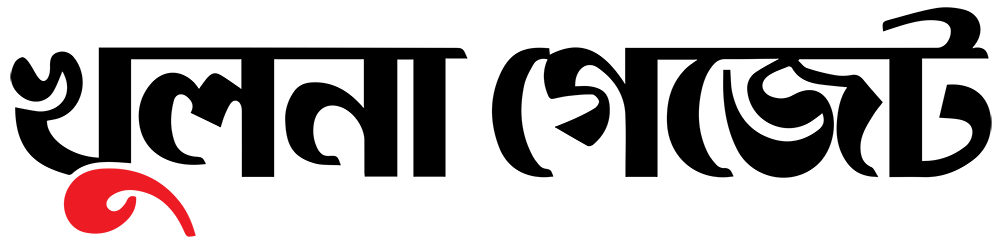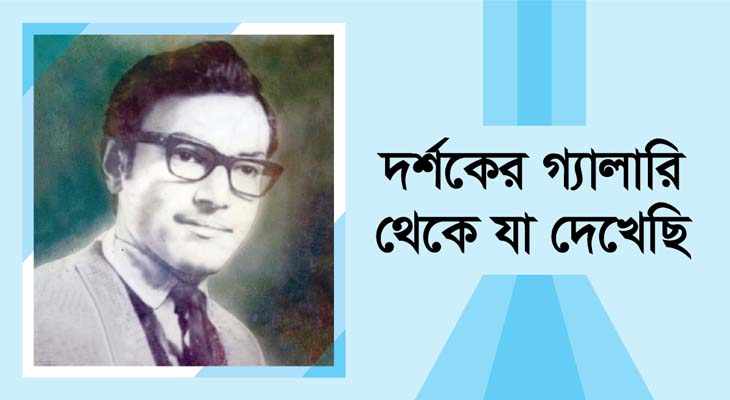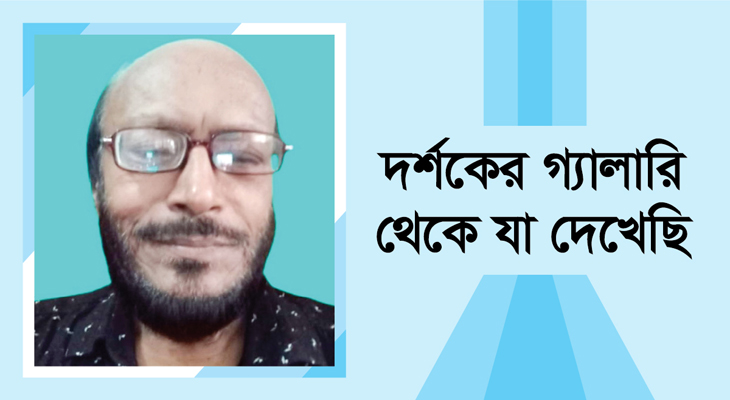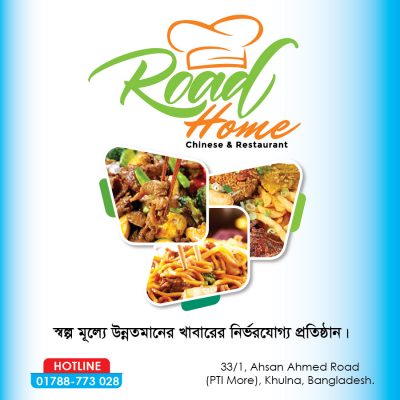ইংরেজি ‘পলিটিক্স’ শব্দের বাংলা অর্থ ‘রাজনীতি’ হিসেবে আমরা সবাই ধরে নেই। কিন্তু এই দুটি শব্দের উৎপত্তি নিয়ে একটু গভীরে গেলে শব্দ দুটির পার্থক্য ও দ্বন্দ্বের জটিল সমীকরণ ধরা পড়ে। তাই প্রথমে পলিটিক্স ও রাজনীতি শব্দ দুটির উৎপত্তি নিয়ে সামান্য ধারণা নেওয়া যাক।
গ্রিক Polis (πόλις) অর্থ: নগর-রাষ্ট্র / শহর। তখন প্রাচীন গ্রিসে ছোট ছোট স্বাধীন নগর-রাষ্ট্র ছিল।
গ্রিক Politēs (πολίτης) অর্থ: নাগরিক / নগর-রাষ্ট্রে বসবাসকারী মানুষ।
গ্রিক Politika (πολιτικά) অর্থ: নাগরিক বিষয়াবলি/শাসন সংক্রান্ত আলোচনা।
এরিস্টটলের বিখ্যাত গ্রন্থ ‘Politika’
লাতিন Politicus অর্থ: রাষ্ট্র সংক্রান্ত বা প্রশাসনিক বিষয়। গ্রিক থেকে লাতিনে প্রবেশ।
ফরাসি Politique অর্থ: শাসন / রাষ্ট্রনীতি। মধ্যযুগে ব্যবহৃত রূপ।
ইংরেজি Politics অর্থ: শাসন, রাষ্ট্রনীতি। ক্ষমতার ব্যবহার আধুনিক রূপ।
বাংলায় পলিটিক্স অর্থ: রাজনীতি।
অর্থাৎ ‘পলিটিক্স’ শব্দের মূল শিকড় গ্রিক ‘Polis’ (নগর-রাষ্ট্র) থেকে এসেছে, আর ধাপে ধাপে ভাষাগত পরিবর্তনের মাধ্যমে আজকের ব্যবহৃত রূপে নিয়েছে।
‘রাজনীতি’ শব্দটি এসেছে সংস্কৃত ভাষা থেকে।
এটি দুটি অংশে গঠিত:
১. রাজা → শাসক / শাসনকর্তা।
২. নীতি → নীতিমালা, শাসন পদ্ধতি, আচরণবিধি।
অর্থাৎ রাজনীতি = রাজার শাসননীতি বা রাষ্ট্রশাসনের কৌশল।
প্রাচীন ব্যবহারে ভারতীয় উপমহাদেশে রাজনীতি নিয়ে সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রভাবশালী গ্রন্থ হলো কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র (৪র্থ শতাব্দী খ্রিষ্টপূর্বাব্দ)।
এখানে ‘রাজনীতি শাস্ত্র’ বলতে বোঝানো হয়েছে রাজাকে কীভাবে রাষ্ট্র চালাতে হবে, যুদ্ধনীতি, প্রশাসন, কূটনীতি ও অর্থব্যবস্থা কেমন হবে সেইসব বিষয়।
আধুনিক বাংলা প্রেক্ষাপটে আজকের বাংলায় ‘রাজনীতি’ শব্দটি শুধু রাজার শাসনের সীমায় নেই, বরং এটি রাষ্ট্রব্যবস্থা, গণতন্ত্র, ক্ষমতার ব্যবহার, দলীয় প্রতিযোগিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণসব কিছু মিলিয়েই বোঝানো হয়।
সুতরাং Politics শব্দটি এসেছে গ্রিক Polis → Politika থেকে।
আর রাজনীতি এসেছে সংস্কৃত রাজা + নীতি থেকে।
তাহলে কী দাড়ালো?
‘পলিটিক্স’ শব্দের উৎপত্তি ও প্রয়োগে সরাসরি মানুষের বা নগরের কল্যাণ বিষয় জড়িত। আর ‘রাজনীতি’ শব্দের সাথে রাজা ও রাজকার্য বিষয় জড়িত। সুতরাং এই রাজনীতি থেকে রাজার কল্যাণ হলেও হতে পারে, কিন্তু মানুষ বা জনগণের কল্যাণ আশা করা যায় না। অতএব আমাদের দেশে যারা রাজনীতি করে তারা নিজেকে রাজা বা রাজা বিষয়ক কিছু একটা মনে করাই স্বাভাবিক। তাদের কাছে জনগণ বা মানুষের কল্যাণ আশা করা যায় না। তারা রাজার মতো ক্ষমতাশালী হতে রাজনীতি করবে এটাই স্বাভাবিক। আর যেসব দেশের নেতারা পলিটিক্স করে তারা জনগণের ও দেশেরথ কল্যাণে কাজ করার জন্য পলিটিক্স করবে সেটাও স্বাভাবিক। কারণ তারা জানে পলিটিক্স শব্দের অর্থ কী। তেমনি আমাদের দেশের নেতারাও জানে রাজনীতি শব্দের অর্থ কী। অতএব আমাদের দুঃখ করার কিছু নেই। তেঁতুল গাছের বীজ রোপণ করে সেই গাছে কমলা আশা করা মানে বোকার স্বর্গে বসবাস করা। জন্ম যার যেমন, কর্ম তার তেমন হওয়াই স্বাভাবিক।
গ্রীক, পলিশ, লাতিন, ইংরেজরা করে ‘পলিটিক্স’, আর আমরা করি ‘রাজনীতি’। পলিটিক্স করার অর্থ দাড়ায় রাজ্য বা নগর শাসন, আর রাজনীতি করার অর্থ দাড়ায় রাজার কাজকর্ম। যারা পলিটিক্স করে তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে- রাজ্য বা দেশ বা দেশের মানুষকে সঠিকভাবে পরিচালনা করাই পলিটিসিয়ানের মূল দায়িত্ব। জন্ম থেকে পলিটিক্সের সাথে জড়িত মানুষেরা সেভাবে নিজেকে গড়ে তোলে। দেশের স্বার্থে, নগরের স্বার্থে, দেশের মানুষের স্বার্থে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া পলিটিসিয়ানদের দায়িত্ব বলে তারা ধরে নেয়। তাইতো হাজার হাজার বছর ধরে পলিটিসিয়ানরা তাদের দেশকে গড়ে তুলেছেন আদর্শ ও উন্নত রাষ্ট্র বা নগর হিসেবে। ঐসব দেশের জনগণ পলিটিসিয়ানদের উপর দেশ বা নগর পরিচালনার ভার দিয়ে নিজেরা ভারমুক্ত থাকে। পলিটিসিয়ানরাও তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যান ও জনগণের আশা আকাক্সক্ষা পূরণের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। ঐসব দেশের পলিটিসিয়ানরা কখনো বিপথগামী হলে পলিটিক্স শব্দের অর্থ অনুধাবন করে নিজেই আসন ছেড়ে জাতি ও জনগণের কাছে আত্মসমর্পণ করে পলিটিক্সের মর্যাদা অক্ষুণœ রাখেন।
পক্ষান্তরে যারা ‘রাজনীতি’ করেন তারা রাজনীতি শব্দের অর্থ জেনেই রাজার মতো ভাব নিয়ে চলেন। রাষ্ট্র, নগর বা রাষ্ট্রের মানুষ নিয়ে চিন্তা করা তাদের দায়িত্ব বলে মনে করেন না। বরং রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে রাজার মতো চলাই তাদের অধিকার বলে মনে করেন। বাঘ সিংহ যেমন মনে করে তারা বনের রাজা, রাজনীতির লোকেরা তেমনি তাদেরকে দেশের রাজা মনে করেন। বাঘ সিংহ কখনোই চায় না যে, তার বনে অন্য কোন প্রাণী রাজত্ব করুক। তেমনি রাজনীতির লোকেরাও চান না যে, তার দেশে অন্য কোন মানুষ রাজনীতি করুক। এটাই পলিটিক্স ও রাজনীতি করা মানুষের মৌলিক দ্বন্ধ। তাই পলিটিসিয়ানদের কাছে তাদের সংশ্লিষ্ট দেশ ও দেশের জনগণের ভাগ্য গড়ে, আর রাজনীতিবিদের কাছে সংশ্লিষ্ট দেশ ও দেশের জনগণের ভাগ্য হয় লাঞ্ছিত। জনগণ তাদের কাছে দাবার গুটি বৈ অন্য কিছু নয়।
বাংলাদেশ কাগজে কলমে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। স্বাধীনতার পর থেকে গণতন্ত্রকে ভিত্তি করে রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার বুলি আওড়ানো হয়। কিন্তু স্বাধীনতার পাঁচ দশক পার হলেও রাজনীতির সংস্কৃতি এখনও সুসংহত ও জনগণমুখী হয়নি। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দুর্নীতি, সহিংসতা ও ভিন্নমত দমন জাতীয় রাজনীতিকে জটিল করে তুলেছে।
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
বাংলাদেশের রাজনীতি মূলত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে সূচনা হয়। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পর জনগণের প্রত্যাশা ছিল গণতান্ত্রিক ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা। কিন্তু স্বাধীনতার অল্পদিনের মধ্যেই একদলীয় শাসন, সামরিক শাসন, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বারবার ক্ষমতা পরিবর্তন রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে কলুষিত করেছে।
১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক হত্যাকা-, ১৯৮০ দশকের সামরিক শাসন, ১৯৯১ সালে বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা এবং পরবর্তীতে আবার যে লাউ সেই কদু। এসব ঘটনাই প্রমাণ করে, বাংলাদেশের রাজনীতি ধারাবাহিক গণতন্ত্র ও সুশাসনের পথে এগোতে পারেনি।
বাংলাদেশের রাজনীতির প্রধান খারাপ দিক
১. দলীয় স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে রাখা: রাজনীতির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত জনগণের সেবা। কিন্তু বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলো প্রায়ই নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখা বা প্রতিপক্ষকে দুর্বল করার স্বার্থে নীতি নির্ধারণ করে। ফলে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় ধারাবাহিকতা থাকে না।
২. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে দুর্নীতির উচ্চন্তরে রয়েছে। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে সরকারি চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, টেন্ডার ও প্রকল্পে স্বজনপ্রীতি দেখা যায়। এতে যোগ্যতা ও দক্ষতার অবমূল্যায়ন ঘটে।
৩. সহিংসতা ও রাজনৈতিক সংঘাত: রাজনীতির অন্যতম বড় সমস্যা হলো সহিংসতা। কথায় কথায় হরতাল, অবরোধ, দলীয় সন্ত্রাস, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলে। ছাত্ররাজনীতিতেও সহিংসতার প্রভাব গভীর।
৪. গণতান্ত্রিক চর্চার অভাব: রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুপস্থিত। সিদ্ধান্ত গ্রহণ একক নেতার ওপর নির্ভরশীল। তৃণমূল নেতাদের অংশগ্রহণ সীমিত। এর ফলে নেতৃত্বের মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি গড়ে ওঠে না।
৫. ভিন্নমতের প্রতি অসহিষ্ণুতা: বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভিন্নমত প্রকাশ করলে তাকে প্রতিপক্ষ নয়, বরং শত্রু মনে করা হয়। এর ফলে সংলাপ, সমঝোতা ও রাজনৈতিক সহনশীলতা নষ্ট হয়।
৬. রাজনীতির বাণিজ্যিকীকরণ: অনেকেই রাজনীতিকে পেশা নয়, বরং ব্যবসা হিসেবে ব্যবহার করেন। রাজনীতিতে প্রবেশের মূল উদ্দেশ্য হয় অর্থ উপার্জন, জমি দখল, প্রভাব বিস্তার ও ক্ষমতার অপব্যবহার।
৭. শিক্ষা, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থায় রাজনৈতিক প্রভাব: রাজনৈতিক দলগুলো বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থায় প্রভাব খাটিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে। এর ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের নিরপেক্ষতা ক্ষুন্ন হয় এবং জনগণের আস্থা নষ্ট হয়।
৮. দুর্বল সুশাসন ও আইনের শাসন: আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ঘাটতি অন্যতম সমস্যা। ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা প্রায়ই আইন ভঙ্গ করলেও শাস্তি এড়াতে সক্ষম হয়। এতে সাধারণ জনগণের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়।
তুলনামূলক আলোচনা
অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ যেমন মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ভারত ইত্যাদির তুলনায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দুর্বল। সিঙ্গাপুরের মতো দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সুশাসন অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করেছে। কিন্তু বাংলাদেশে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বারবার বাধাগ্রস্ত করছে।
সমস্যার মূল কারণ
১. রাজনৈতিক সংস্কৃতির অপরিপক্কতা।
২. দারিদ্র ও সামাজিক বৈষম্য।
৩. শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতা।
৪. আইনের শাসনের অভাব।
৫. রাজনৈতিক নেতাদের দায়বদ্ধতার ঘাটতি।
সমাধানের উপায়
১. গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা দলীর ভেতরে গণতান্ত্রিক ভোট, মতামত গ্রহণ ও নেতৃত্ব পরিবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি।
২. দুর্নীতি দমন দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করা এবং কমিশনের অভ্যন্তরে স্বচ্ছতা আনয়ন করা।
৩. রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ আইনের কঠোর প্রয়োগ এবং সহিংস রাজনীতিকে নিরুৎসাহিত করা।
৪. ভিন্নমতের প্রতি সহিষ্ণুতা সংলাপ ও আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করা।
৫. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা প্রার্থী মনোনয়ন, সরকারি বাজেট ও প্রকল্পে স্বচ্ছতা আনয়ন।
৬. শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি নাগরিকদের রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়ানো এবং নৈতিক শিক্ষা বিস্তার।
উপসংহার : বাংলাদেশের রাজনীতিতে গণতন্ত্রের চর্চা ও উন্নয়নের সম্ভাবনা থাকলেও রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্নীতি, সহিংসতা ও অসহিষ্ণুতা একটি বড় বাধা। খারাপ দিকগুলো চিহ্নিত করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করলে রাজনীতি হতে পারে স্বচ্ছ, গণমুখী এবং উন্নয়ন বান্ধব। সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন জনগণের সচেতন অংশগ্রহণ, নেতাদের দায়বদ্ধতা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। তবেই বাংলাদেশ রাজনীতির খারাপ দিকগুলো কাটিয়ে উঠে একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।
লেখক : সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা।
খুলনা গেজেট/এনএম