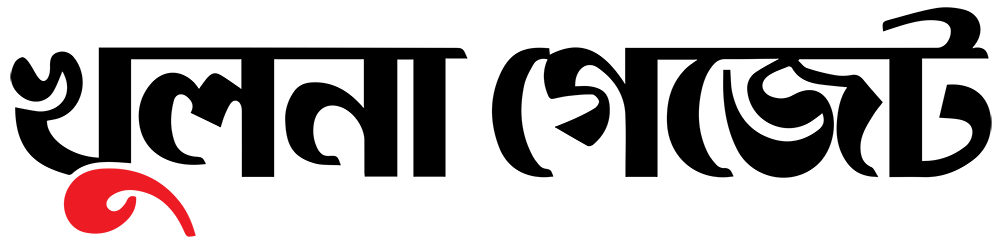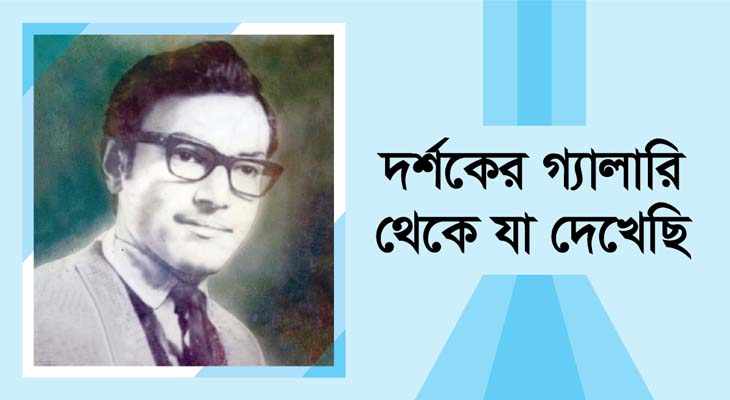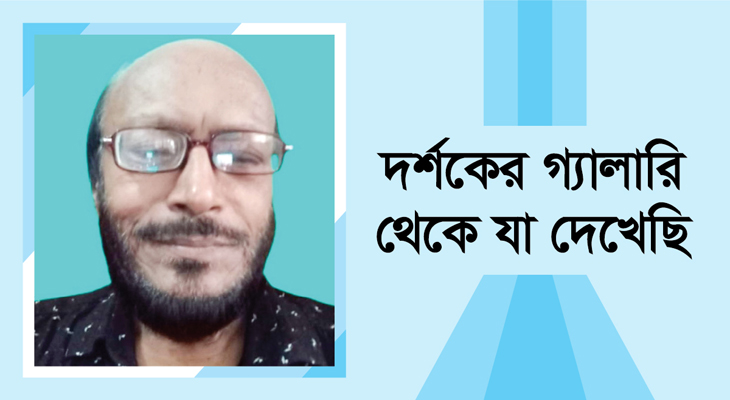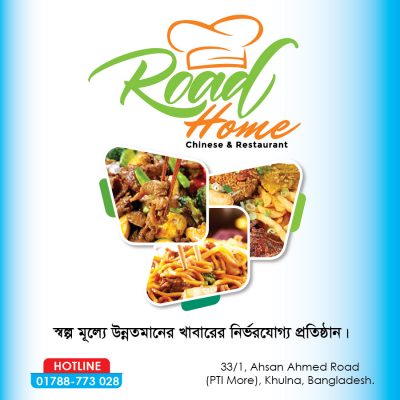খুলনা গেজেট নামের নিউজ পোর্টালটি দৈনিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আনন্দিত হলাম। রাষ্ট্রীয় কিংবা আন্তর্জাতিক খবর বা তথ্যাদি পাবার জন্য দেশে প্রচুর খবরের কাগজ আছে। চট্টগ্রাম অঞ্চল এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কয়েকটা শক্তিশালী পত্রিকাও আছে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল তথা খুলনা অঞ্চলে দৈনিক পত্রিকা আছে, কিন্তু এই অঞ্চলের ‘সমস্যা, সংকট, সম্ভাবনা ও সাফল্য’ নিয়ে আরও বিস্তারিত রিপোর্টিং- এর প্রয়োজন আছে। তাই খুলনা গেজেটকে স্বাগতম জানাচ্ছি।
এবার আসি এই অঞ্চলের সংকট ও সম্ভাবনার বিষয়ে। বাংলাদেশ এখন যে অবস্থানে পৌঁছেছে, তাতে ভবিষ্যতে সম্ভাব্য সংকট ও সাফল্যের সম্ভাবনা নিয়ে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা প্রয়োজন। প্রথমেই সংকটের কথা বলি। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে সমগ্র বিশ্বজুড়ে যে সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে, তার প্রভাবে খুলনা অঞ্চল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এখানে বলে নেওয়া ভালো যে, খুলনা অঞ্চল বলতে আমি বৃহত্তর খুলনাকে বোঝাচ্ছি।
সংকটের প্রধান উপাদান তিনটি হচ্ছে প্রথমত, স্বাভাবিক আবহাওয়ায় ধীরে ধীরে বিপুল মাত্রায় পরিবর্তন আসবে। এখন থেকেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যে ঋতুগুলোর স্বাভাবিক সময়কাল বদলে যাচ্ছে। ছয় ঋতুর বাংলাদেশ থেকে হেমন্তকাল আর শরৎকাল এখন আর অনুভূত হচ্ছে না। গ্রীষ্মে কিছু সময় তীব্র তাপদাহে মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে। এই বিপদের কারণে খুলনা অঞ্চলও ভুগছে। বর্ষায় বৃষ্টির নিয়ম এখন আর দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ করে অল্প সময়ে প্রচুর বৃষ্টির ঘটনা ঘটছে। এতে শহরগুলোতে জলাবদ্ধতা বাড়ছে। এমন মৌসুমে খরার আশঙ্কা বাড়ছে। আবার ওই বৃষ্টির কারণে হঠাৎ স্থানীয় পর্যায়ে বন্যার আশঙ্কা হচ্ছে। শীতকাল ছোট হয়ে আসছে, কিন্তু মাঝে মাঝে কয়েকদিন তীব্র শীত পড়তে পারে। আবহাওয়ার এই অস্থিরতা এবং অনিশ্চয়তা ক্রমেই বাড়তে থাকবে।
সংকটের দ্বিতীয় উপাদান হচ্ছে উপকূলীয় সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি এবং এর ফলস্বরূপ উপকূল অঞ্চলে নদ-নদী, খাল-বিলের পানি লবণাক্ত হয়ে যাওয়া। বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যৎবাণী করছেন যে এখন থেকে ২০-৩০ বছরের মধ্যে একেবারে উপকূলীয় উপজেলাগুলোর পানির লবণাক্ততার মাত্রা সমুদ্রের মাত্রায় পৌঁছাবে। ইতিমধ্যেই হয়তো সমুদ্রের পানির স্বাভাবিক স্তরের তুলনায় এখন পানির স্তর এক ফুটের কাছাকাছি বেড়ে গেছে। বৃহত্তর খুলনা জেলায় এই লবণাক্ততার প্রভাবে মানুষ কষ্ট পাচ্ছে। খাবার পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। সবচেয়ে গরিব মানুষকেও খাবার পানি কিনে খেতে হচ্ছে। লবণাক্ততার প্রভাবে কৃষি খাত মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। শুধু বৃষ্টির পানির উপর নির্ভর করে ফসল উৎপাদন ঝুঁকির মুখে পড়বে এবং উৎপাদনের মাত্রা কমে যাবে। লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে এমন ফসল ইতিমধ্যেই চাষ শুরু হয়েছে। যেমন- ভুট্টা, সূর্যমুখী এবং তরমুজ এই অঞ্চলের নতুন ফসল। অর্থাৎ, লবণাক্ততা আরও বাড়ার আশঙ্কা মোকাবিলার জন্য দুটি বড় ধরনের কাজ করতে হবে।
প্রথমত, সুপেয় পানির সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে এবং দরিদ্রদের মধ্যে তার প্রাপ্যতা বাড়াতে হবে। এই কাজে প্রতিটি পোল্ডারের মধ্যে যে বিলগুলো আছে, সেগুলো পুনরুদ্ধার করে তাদের গভীরতা বাড়িয়ে জলাধার সৃষ্টি করতে হবে। আমার ধারণা মতে, এই জমিগুলোর অধিকাংশই সরকারি খাস জমি। তাহলে উপকূলের মানুষগুলোকে বাঁচানোর জন্য এগুলো উদ্ধার করে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার জন্য জলাধার হিসেবে সংস্কার করতে হবে।
দ্বিতীয়ত, কৃষি ক্ষেত্রে শস্যের পর্যায়ক্রম নিয়ে ভাবতে হবে, অর্থাৎ বৃষ্টির পানির উপর নির্ভরশীলতা বাড়াতে হবে। যদিও বৃষ্টিপাতের সময়কাল অনিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে।
এবার দ্বিতীয় সংকটের কথায় আসি। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে আরেকটি সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে। সেটি হলো ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা এবং সংখ্যা, দুটোই বাড়ছে এবং আরও বাড়বে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো আমরা আইলা কিংবা সিডরের মতো আরও জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ের দুর্ভোগে পড়ব। এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সারা পৃথিবী জুড়েই বাড়ছে। এর মূল কারণ সমুদ্রের তাপমাত্রা বাড়লে প্রচুর ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়। একে ঠেকানোর কোনো উপায় নেই, তবে এর ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। গত শতাব্দীর ষাটের দশকে খুলনা এলাকা তথা উপকূলজুড়ে পোল্ডার বা বেড়িবাঁধ নির্মিত হয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জোয়ারের সামান্য চাপেই এগুলো প্রায়ই ভেঙে যাচ্ছে। এগুলোকে আরও উঁচু করে এবং আরও শক্তিশালী করে পুননিমার্ণ প্রয়োজন। বেড়িবাঁধ এলাকার ভেতরে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের জন্য প্রচুর রেগুলেটরের প্রয়োজন হবে। এখন যে রেগুলেটরগুলো দেখা যায়, সেগুলোর প্রায় সবই অকেজো। অর্থাৎ, প্রযুক্তি পরিবর্তন করে এগুলোকে পুননিমার্ণ করতে হবে এবং এর পরিচালনার দায়িত্ব স্থানীয় জনসাধারণকে দিতে হবে।
যদি তৃতীয় সংকটের কথায় আসি, তা হচ্ছে উপকূল অঞ্চলের মানুষের মাইগ্রেশন বা অভিবাসন। উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষগুলো ইতিমধ্যেই অন্যত্র দেশে-বিদেশে চলে যেতে শুরু করেছেন। কারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে নিরাপত্তা নেই এবং কর্মসংস্থানের বিরাট অভাব। এ কারণেই নগরায়নের প্রক্রিয়া আরও দ্রুত হবে। আমাদের দেশে নগরায়নের জন্য কোনো পরিকল্পনা নেই। কাজেই সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাটসহ বিভিন্ন থানা-শহরের জনসংখ্যা দ্রুত বাড়বে। এই অভিবাসী মানুষ হয়তো ঢাকা বা চট্টগ্রামের মতো বড় শহরগুলোতেও আশ্রয় নেবে, কিন্তু তাদের নিজস্ব এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা গেলে তারা হয়তো দেশান্তরি হতেন না।
এবার কিছু সম্ভাবনার কথা বলি। প্রথম সম্ভাবনার বিষয়টি হচ্ছে পর্যটন। দেশের গর্ব সুন্দরবনের অবস্থান এই তিনটি জেলার দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে। সারা দেশের মানুষ সুন্দরবনে ভ্রমণের জন্য আগ্রহী। এই সম্ভাবনাটি সুচারু পরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তবায়িত করতে হবে। যদি ভ্রমণকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়, নিরাপদে রাত কাটানোর ব্যবস্থা করা যায় এবং বনভূমির ভেতরে চলাচলের সু-ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আগমন বৃদ্ধি পাবে এবং স্থানীয় অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে। তবে এই কাজে পরিবেশ সম্মত পর্যটন বা ইকো-ট্যুরিজমের ব্যবস্থা থাকতে হবে। পরিকল্পিতভাবে ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে পারলে পাশের দেশ তো বটেই, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও ভ্রমণকারীরা আসবে। পৃথিবীর বহু দেশে তাদের মোট জাতীয় আয়ের ৫০/৮০ ভাগ পর্যটন থেকে পেয়ে থাকে।
দ্বিতীয় সম্ভাবনা হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাত্রা বাড়িয়ে শিল্পায়নের সম্ভাবনাকে জোরদার করা। এখন থেকে ৫০-৬০ বছর আগে বেশ কিছু বড় শিল্প গড়ে উঠেছিল খুলনা অঞ্চলে। এখনও শিল্পায়নের সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল বলে আমি মনে করি। পদ্মা সেতু খুলনা অঞ্চলকে দেশের সাথে যুক্ত করেছে। নৌপথের সংযোগকে আরও উন্নত করা যায়। আমি যখন ছাত্র ছিলাম, তখন বহুবার ঢাকা থেকে ‘রকেট’- এ চড়ে খুলনায় এসেছি। মংলা নালা (নদী) উন্নয়ন করতে পারলে নৌ চলাচলের এই রুটটি খোলা রাখা যায়। সড়ক বা রেল যোগাযোগের উন্নতি হলে নৌপথে মানুষের চলাচল কমে আসে। তবে, অপচিনশীল শিল্পজাত পণ্য পরিবহনে নৌচলাচলের মতো সাশ্রয়ী যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। বাগেরহাটে নির্মীয়মাণ বিমানবন্দরটিকেও চালু করা যেতে পারে। ষাট গম্বুজ মসজিদকে কেন্দ্র করে পর্যটনকে নজরে আনা যায়।
তৃতীয় সম্ভাবনা হচ্ছে সামুদ্রিক পথে বহির্বিশ্বের সাথে দেশের যোগাযোগ। আমি মংলা বন্দরের কথা বলছি। বাংলাদেশে চট্টগ্রাম, পায়রা ও মংলা এই তিনটি প্রধান নৌবন্দর। মহেশখালীর কাছে মাতারবাড়িতে যে নৌবন্দরটি নির্মিত হচ্ছে সেটি সম্ভাবনাময়, কারণ এখানে গভীর সমুদ্র থেকে অনেক বেশি ড্রাফটের জাহাজ আসতে পারবে। দীর্ঘ মেয়াদে চট্টগ্রাম, পায়রা এবং মংলা এই তিনটি বন্দরের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়, কারণ এখানে যে জাহাজ ঢুকতে পারে তার গভীরতা ২২/২৪ ফুটের বেশি নয়। এই তিনটি বন্দরে কয়েক বছর পরপর হাজার কোটি টাকা খরচ করতে হয়। ঘন ঘন ড্রেজিং না করলে ওই গভীরতাও কার্যকর থাকে না, অথচ বিশ্বজুড়ে সমুদ্রগামী জাহাজের জন্য ৫০-৬০ ফুট গভীরতা প্রায় অপরিহার্য। এই সম্ভাবনাটি মংলায় রয়েছে। পঞ্চাশের দশকে সামান্য খরচ কমানোর জন্য মংলা বন্দরের স্থান ভুল জায়গায় স্থির করা হয়েছিল। এটি নির্মাণ করা উচিত ছিল চালনায়। এখনো যদি বর্তমান মংলা শহরের দক্ষিণ বানিশান্তা বা হারবাড়িয়ায় স্থির করা যায়, তাহলে অনেক বেশি ড্রাফট সম্পন্ন জাহাজ সহজেই ভিড়তে পারবে।
বর্তমানে মংলাকে কেবল রপ্তানির জন্য ব্যবহার করা হয়, কিন্তু সহজেই একে আমদানি ও রপ্তানি দুইয়ের জন্যই উপযোগী করা যায়। বড় জাহাজ থেকে মাল নামিয়ে উপকূলীয় নৌপথে চট্টগ্রাম, ঢাকা কিংবা নারায়ণগঞ্জ, আরিচা কিংবা সিরাজগঞ্জ, অথবা চাঁদপুর কিংবা আশুগঞ্জ সহজেই নিয়ে যাওয়া যায়। বর্তমানে মংলা বন্দরে যে গুদামগুলো তৈরি আছে সেগুলোকেও কাজে লাগানো যেতে পারে, কারণ নৌপথের সাথে রেলপথ সঠিকভাবে সংযুক্ত করা গেলে তা নেপাল কিংবা ভুটানের কাজেও আসবে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ আশুগঞ্জকে ব্যবহার করছে। মংলা বন্দর ব্যবহারের জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা যেতে পারে।
সংকট ও সম্ভাবনা নিয়ে কয়েকটি কথা লিখলাম। পরবর্তীতে এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও লেখা তৈরির ইচ্ছা রইল।
লেখক: এমেরিটাস অধ্যাপক, সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ সেন্টার (ঈ৩ঊজ), ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়।
খুলনা গেজেট/এএজে