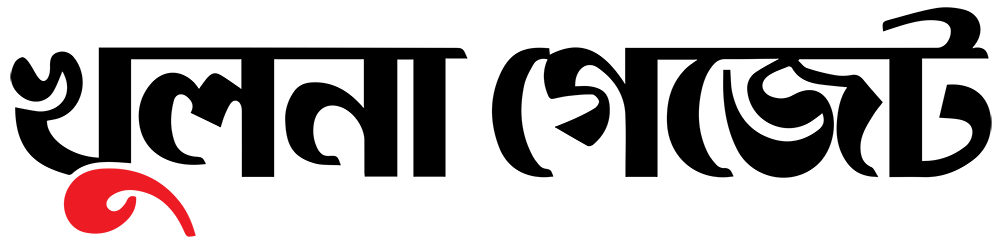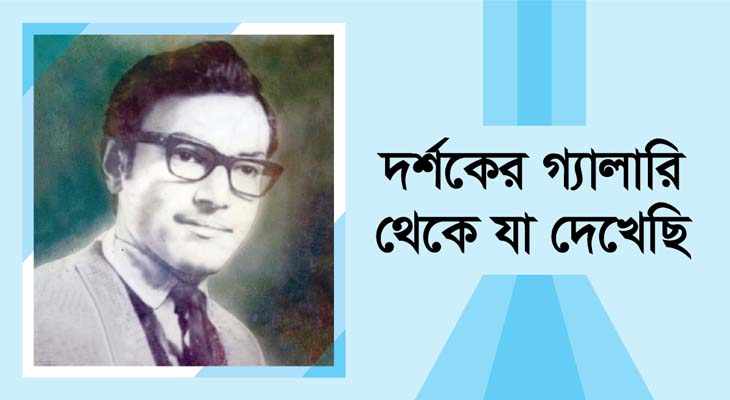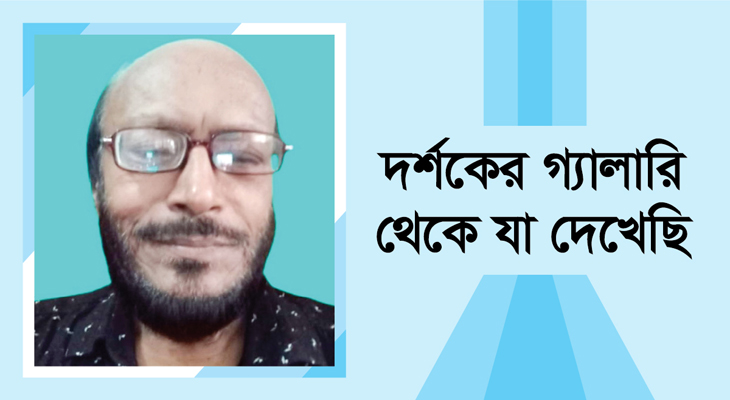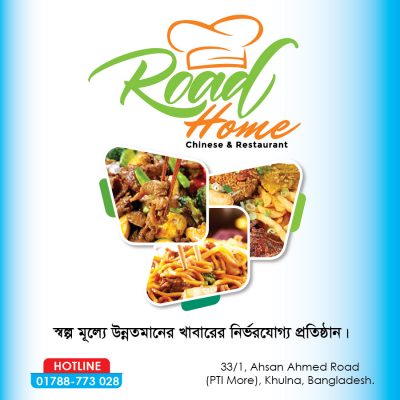বাংলাদেশ যখন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রতিষ্ঠা লাভ করছে, তখন দেশের উপকূলীয় অঞ্চল এখনও অবহেলার শিকার। বঙ্গোপসাগরের কোলে অবস্থিত এই অঞ্চল শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভান্ডার নয়, বরং দেশের অর্থনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি। তবুও, উন্নয়ন নীতি, বিনিয়োগ ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এটি প্রায়শই গৌণ ভূমিকা পালন করে। দেশের জিডিপির প্রায় ২৫% এবং জনসংখ্যার প্রায় ২৮% নিয়ে গঠিত এই অঞ্চলের উন্নয়ন উপেক্ষা করে কোনো জাতীয় উন্নয়ন কল্পনা করা অবাস্তব।
বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের দৈর্ঘ্য প্রায় ৭১০ কিলোমিটার, যার মধ্যে ৩১০ কিলোমিটার সমতল ও সমুদ্রসৈকত, ১২৫ কিলোমিটার সুন্দরবন এবং ২৭৫ কিলোমিটার নদীর মোহনা ও দ্বীপমালা রয়েছে। টেকনাফ থেকে শুরু করে সাতক্ষীরা পর্যন্ত বিস্তৃত এই অঞ্চলে অবস্থিত দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রাম ও মোংলা, বিশ্বেও সেরা ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন এবং বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘতম অখণ্ডিত সমুদ্রসৈকত কক্সবাজার। এই সম্পদ শুধু প্রাকৃতিক নয়, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও জীববৈচিত্রের দিক থেকেও অপরিহার্য। তাই এই অঞ্চলের উন্নয়ন না হলে দেশের টেকসই উন্নয়ন অসম্ভব।
উপকূলীয় অঞ্চল জলবায়ু পরিবর্তনের প্রথম ও প্রত্যক্ষ শিকার। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং নদীভাঙন এই অঞ্চলের মানুষের জীবিকা ও বসবাসকে ক্রমাগত হুমকির মুখে ফেলছে। ১৭৯৭ থকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ৪৭৮ বার মাঝারি ও বড় ধরনের জলোচ্ছ্বাস এবং ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের উপকূলকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। স্বাধীনতার পর গত ৪০ বছরে ১৪৯ টি ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস ঘটেছে, যা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘনত্ব বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। ২০২৩ সালের ঘূর্ণিঝড় মোখা এবং ২০২৪ সালের ঘূর্ণিঝড় রিমাল উপকূলীয় অঞ্চলের জনজীবন ও অবকাঠামোতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়েছে। রিমালের আঘাতে ১৯ টি জেলায় প্রায় ৩২ লাখ শিশু ঝুঁকির মুখে পড়েছিল।
এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবে লাখ লাখ মানুষ ভিটেমাটি হারিয়ে অন্যান্য অঞ্চলে স্থানান্তরিত হচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০৫০ সালের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের ১ কোটি ৩৩ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হতে পারে।
ইন্টারন্যাশনাল ডিসপ্লেসমেন্ট মনিটরিং সেন্টার (ওউগঈ)-এর ২০২৪ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ বিশ্বের পঞ্চম সর্বোচ্চ অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত দেশ। ২০০৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ১ কোটি ৭০ লাখ মানুষ দুর্যোগের কারণে ঘরছাড়া হয়েছে। এর মধ্যে উপকূলীয় অঞ্চল থেকে আসা মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। ঢাকার বস্তির প্রায় ৪০ বাসিন্দা উপকূলীয় অঞ্চল থেকে আসা বলে একটি সমীক্ষা বলছে।
কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষি অর্থনীতি নিম্নমুখী। লবণাক্ততা বৃদ্ধি, পানির অপ্রতুলতা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে চাষাবাদযোগ্য জমি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৪৮ থকে ১৯৯৭ সালের মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে শস্য উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ হলেও উপকূলীয় অঞ্চলে তা কমেছে।
তবুও এই অঞ্চলে কৃষির অপার সম্ভাবনা রয়েছে। লবণাক্ত জমিতে উপযোগী ফসল উদ্ভাবন, হাইব্রিড বীজের ব্যবহার, সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফলন পার্থক্য কমানো সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, উপকূলীয় অঞ্চলে পুঁইশাকের গড় ফলন ১৫.৯৪ মেট্রিক টন/হেক্টর, কিন্তু উত্তম ব্যবস্থাপনায় তা ৪০-৫০ মেট্রিক টনে উন্নীত করা যায়। একইভাবে ফল চাষে নারিকেল, কলা, আমড়া ও পেয়ারার উৎপাদন বাড়ানো যায়। দেশের উৎপাদিত পেয়ারা ও আমড়ার ৮০% উপকূলীয় অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। এছাড়াও, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে এই অঞ্চলের সম্ভাবনা অফুরন্ত, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল ভিত্তি হতে পারে।

উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। যদিও ২০০৩ সালে ইন্টিগ্রেটেড কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (ওঈতগচ)-এর মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চল নীতি ২০০৫ সালে অনুমোদিত হয়, তবুও এর বাস্তবায়ন অসম্পূর্ণ। বর্তমানে একটি সমন্বিত উপকূল উন্নয়ন বোর্ড গঠনের দাবি উঠেছে। বেসরকারি সংস্থাগুলো দাবি করছে যে নদীভরাট, জলাবদ্ধতা ও জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় একটি শক্তিশালী সংস্থা প্রয়োজন।
আরেকটি বড় সমস্যা হলো তথ্যের অভাব ও সমন্বয়হীনতা। উপকূলীয় অঞ্চল সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য থাকলেও তা সমন্বিত নয়। একটি সমন্বিত জ্ঞানভান্ডার গড়ে তোলা হয়েছে মেঘনা মোহনার জন্য, কিন্তু সারা উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য এটি প্রসারিত করা প্রয়োজন।
বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল শুধু কৃষি ও মৎস্য উৎপাদনের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং বাণিজ্য, পর্যটন, শক্তি উৎপাদন এবং পরিবেশ সংরক্ষণেও এটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। কক্সবাজার পর্যটন শিল্পের জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি পাচ্ছে। সুন্দরবন হচ্ছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার ও অসংখ্য প্রজাতির আশ্রয়স্থল। মৎস্য চাষ, প্রাণিসম্পদ ও বিকল্প কৃষি এখানকার মানুষের জীবিকার মূল ভিত্তি। মাতারবাড়ির মতো বড় আকারের বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পগুলো এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক চেহারা পাল্টে দিতে পারে।
টেকসই উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ
উপকূলীয় অঞ্চলের টেকসই উন্নয়নের জন্য সুশীল সমাজ ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবি জানিয়েছে। এসব দাবি বাস্তবায়নে সরকারকে দীর্ঘমেয়াদী ও সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এর মধ্যে অন্যতম হলো:
উপকূল উন্নয়ন বোর্ড গঠন : উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯ টি জেলার সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করে সমন্বিত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য একটি বিশেষ ‘উপকূল উন্নয়ন বোর্ড’ গঠন করা জরুরি। এই বোর্ড জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজটি করবে।
টেকসই বেড়িবাঁধ নির্মাণ ও সংস্কার : জলোচ্ছ্বাস ও বন্যা থেকে উপকূলবাসীকে রক্ষা করতে টেকসই ও উঁচু বেড়িবাঁধ নির্মাণ এবং পুরাতন বাঁধগুলোর নিয়মিত সংস্কার করা অপরিহার্য। পাশাপাশি বাঁধের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।
সুপেয় পানির স্থায়ী সমাধান: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সুপেয় পানির সংকট মোকাবিলায় রেইনওয়াটার হার্ভেস্টিং, গভীর নলকূপ স্থাপন এবং পানি শোধন প্রযুক্তির মতো টেকসই সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে।
বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি: প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যারা জীবিকা হারাচ্ছেন, তাদের জন্য নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। বিশেষ করে মৎস্য ও কৃষি খাতের বাইরে অন্যান্য শিল্প ও সেবা খাতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।
বৃক্ষরোপণ ও সবুজ বেষ্টনী: উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা জরুরি। এটি একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব কমিয়ে আনবে, অন্যদিকে জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে।
নারীর স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন: লবণাক্ত পানির কারণে নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্যঝুঁকি কমাতে সুপেয় পানির সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং নারীদের স্বাস্থ্যসেবায় বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন।
বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল শুধু কৃষি ও মৎস্য উৎপাদনের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং বাণিজ্য, পর্যটন, শক্তি উৎপাদন এবং পরিবেশ সংরক্ষণেও এটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। কক্সবাজার পর্যটন শিল্পের জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি পাচ্ছে। সুন্দরবন হচ্ছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার ও অসংখ্য প্রজাতির আশ্রয়স্থল। মৎস্য চাষ, প্রাণিসম্পদ ও বিকল্প কৃষি এখানকার মানুষের জীবিকার মূল ভিত্তি। মাতারবাড়ির মতো বড় আকারের বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পগুলো এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক চেহারা পাল্টে দিতে পারে।
সর্বোপরি, বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল শুধু ভৌগোলিক নয়, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য অপরিহার্য। এই অঞ্চলের উন্নয়ন না হলে দেশের টেকসই উন্নয়ন অসম্পূর্ণ থাকবে। জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবেলা, টেকসই কৃষি পদ্ধতি, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, বিনিয়োগ পরিকল্পনা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে উপকূলীয় অঞ্চলকে জাতীয় উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসা জরুরি। কারণ, উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন উপেক্ষা করে কোনো জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়।
লেখক : পিএইচডি গবেষক, কলোরাডো বোল্ডার বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র এবং সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।
খুলনা গেজেট/এএজে