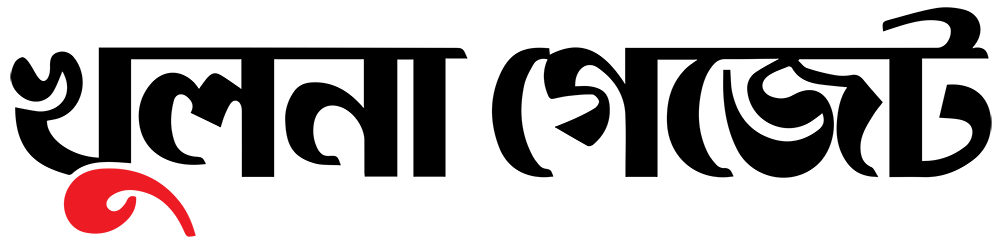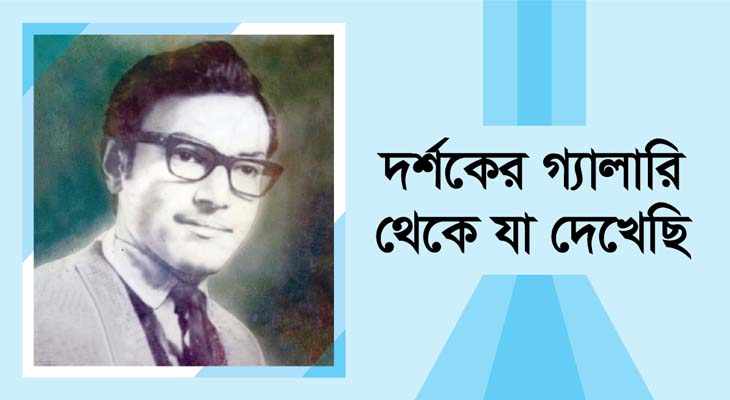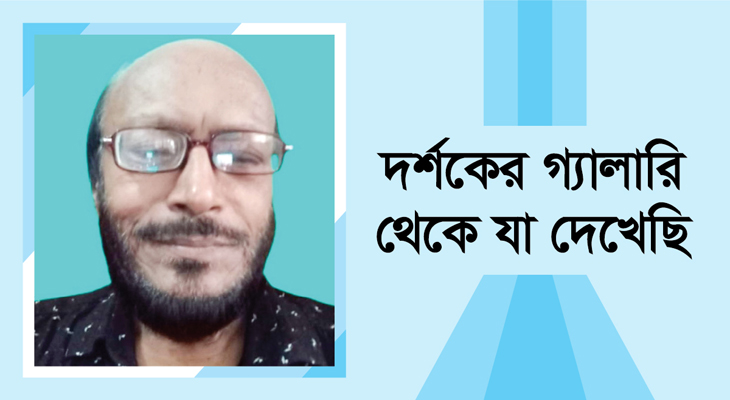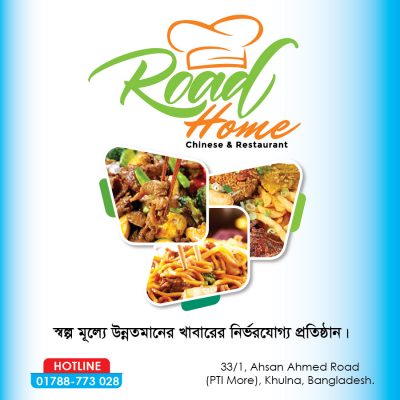বিগত কয়েক দশক ধরে অব্যাহত থাকা ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন ও নগরায়ণের দাপটে আজ বিশ্বপ্রকৃতির অস্তিত্ব হুমকির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। তাই বাড়ন্ত জনসংখ্যার আবাসন সংকট মোকাবেলায় এখন দেদারসে বন উজাড় করছে মানুষ। ট্যুরিজম খাতের বিকাশ সাধনে সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে কাটছে পৃথিবীর নানা প্রান্তের পাহাড়। সঙ্গে শিল্পপতিদের লভ্যাংশ সুরক্ষায় করা হচ্ছে সবুজ উৎপাদন ব্যবস্থার প্রতি অবহেলা। ফলে ক্রমান্বয়ে ঘনীভূত হচ্ছে জলবায়ু সংকট।
এমতাবস্থায়, জলবায়ু, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সরকারি-বেসরকারি সংস্থার প্রচেষ্টায় স্থানীয় সম্প্রদায় তথা দেশের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে জলবায়ু সংকটের ভয়াবহ প্রভাব মোকাবেলায় সচেতন করে সক্রিয়ভাবে পরিবেশ রক্ষার গঠনমূলক কার্যক্রমে নিয়োজিত রাখতে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।
কিন্তু কার্যকরভাবে মানুষকে এ বিষয়ে সচেতন করার সঠিক উপায় কী সেটা বিবেচনা করা এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। কারণ, জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জের (আইপিসিসি) কয়েক শত পৃষ্ঠার রিপোর্ট কিংবা বাতাসে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা (পিপিএম) নিয়ে একজন সাধারণ কৃষক বা দিনমজুর প্রথমেই সরাসরি কোনো আগ্রহ প্রকাশ করবেন না-এটাই স্বাভাবিক। তাকে সারাদিন ‘প্ল্যানেটারি বাউন্ডারি বা বিশ্বপরিবেশ রক্ষায় নির্ধারিত সীমানা’-র নানা দিক সম্পর্কে হাজার বুঝালেও ফলপ্রসূ কিছু না-ও ঘটতে পারে। এখানেই সামনে আসে জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় পরিবেশগত যোগাযোগের ভূমিকা পালনের অনুষঙ্গ।
আদতে, ইউনিভার্সিটি অব ফিলিপাইনের (ওপেন ইউনিভার্সিটি) ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশান স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক আলেক্সান্ডার জি. ফ্লোরের (২০০৪) মতে, পরিবেশগত যোগাযোগ হলো পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও সুরক্ষায় মানুষের মাঝে তথ্য, ধারণা, জ্ঞান বা প্রজ্ঞার সুগঠিত আদান-প্রদান। অর্থাৎ, পরিবেশবিজ্ঞানের সকল জটিল ও দুর্বোধ্য তথ্যগুলোকে সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য করে তোলা এবং সেগুলোকে তাদের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করে উপস্থাপন করাই পরিবেশগত যোগাযোগের কাজ।
এরই অংশ হিসেবে, গতানুগতিক ধারায় ট্রেইনিং বা ক্লাস নেওয়ার বদলে যদি সমুদ্রের তাপমাত্রা বাড়ার কারণে জেলেদের জালে আগের মতো মাছ ধরা না পড়ার কারণ কিংবা দেশের উত্তরাঞ্চলের কৃষকদের গত ১০ বছরে তাদের এলাকায় পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার হার স্যাটেলাইট চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়, তাহলে জলবায়ু পরিবর্তন তাদের কাছে আর কোনো বিমূর্ত ধারণা হয়ে থাকে না। বরং তারা অনুধাবন করেন-এটি তাদের জীবন ও জীবিকার জন্য সংকট সৃষ্টি করছে। এভাবেই সঠিকভাবে কার্যকর যোগাযোগের পদক্ষেপগুলো অনুসরণের মাধ্যমে বিজ্ঞানের ভাষাকে জীবিত ও প্রাণসঞ্চারক করে তোলা সম্ভব।
তাই এই পরিপ্রেক্ষিতে, তরুণ ও যুব সমাজ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং জলবায়ুগতভাবে বিপর্যস্ত এলাকার বাসিন্দাদের মাঝে এমন এক প্রক্রিয়ায় সচেতনতা সৃষ্টি করে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট মোকাবেলার পথ সৃষ্টি করা উচিত, যা তাদেরকে জীবনভর ভাবতে অনুপ্রাণিত করবে। ফলে তারা প্রতিনিয়ত বিষয়টি নিয়ে ভাববে এবং সর্বদা সক্রিয় ভূমিকা পালনের চেষ্টা করবে। এ পর্যায়ে সবচেয়ে কার্যকর পদক্ষেপগুলোর একটি হতে পারে সভা, সেমিনার, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণে মৌখিক স্টোরিটেলিং কৌশলের যথোপযুক্ত প্রয়োগ। এর মধ্য দিয়ে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞদের আবেগ ও অভিজ্ঞতার দ্বৈত মিশেলে গড়ে ওঠা অনন্য ভাষ্যকে জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে পরিবেশগত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখা সম্ভব।
পাশাপাশি, ভিজ্যুয়াল প্রেজেন্টেশন বা স্টোরিটেলিংকেও একটি নিয়ামক কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা যায়। কেননা, মনোবিজ্ঞানী ও নিউরোসায়েন্স বিশেষজ্ঞদের মতে, মানুষ সর্বদা চলমান থাকতে পছন্দ করে। তাই চলমান কোনো দৃশ্য বা চিত্রের মাধ্যমে শেখা বিষয়াদি তাঁর মস্তিষ্কে দীর্ঘস্থায়ী হয়। ফলে লবণাক্ততা বা খরার মতো পরিবেশগত সমস্যার ওপর স্বল্প সময়ের সরল ভিজ্যুয়াল প্রদর্শন দর্শকদের বিষয়টির গভীরে প্রবেশে প্রলুব্ধ করে।
আবার বিশেষজ্ঞদের দাবি, জলবায়ু সংকট নিয়ে প্রতিনিয়ত ভয়াবহতার চিত্র উপস্থাপন মানুষের মাঝে এক ধরনের উদাসীনতা বা ‘ক্লাইমেট ফ্যাটিগ’ তৈরি করতে পারে। এমনকি তাদের মধ্যে এ ধরনের ধারণাও বিস্তৃত হতে পারে যে: “পরিবেশের সবই তো শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমি একা আর কী করব?”
সেই আঙ্গিক থেকে পরিবেশগত যোগাযোগের আরেকটি বড় দায়িত্ব হলো এই নেতিবাচক চিন্তাকে দূর করে তাদের মনে আশার সঞ্চার করা। যা জনসাধারণকে বুঝতে শেখায়, তার একার একটা কাজও কত বড় ভূমিকা রাখতে পারে। সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করলেই জলবায়ুর এই নেতিবাচক পরিবর্তন ঠেকানো যে সহজতর-এটা বোঝানোই পরিবেশগত যোগাযোগের একটা লক্ষ্য।
তাই পরিবেশগত সমস্যার পাশাপাশি সমাধানের গল্পগুলোকেও সামনে নিয়ে আসতে হবে। কারণ, খুলনার পাইকগাছায় লবণাক্ত জমিতে বিশেষ পদ্ধতিতে তরমুজ চাষ করে সফল হওয়া কৃষকের গল্প কিংবা রংপুরের কোনো গ্রামে কমিউনিটি সোলারের মাধ্যমে অর্জিত অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার কথা যখন গণমাধ্যমে প্রচারিত হবে, তখন তা অন্যকেও অনুপ্রাণিত করবে।
জলবায়ু সংকট নিরসনে এভাবে সাধারণ মানুষের মাঝে সচেতনতা তৈরি করা গেলে স্বাভাবিকভাবেই দেশের নীতিনির্ধারকদের ওপর সামাজিক চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। এ ক্ষেত্রে, পরিবেশগত যোগাযোগকেও একটি শক্তিশালী জনমত তৈরির মাধ্যমে পরিণত করা যেতে পারে, যা সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনকে জলবায়ুবান্ধব নীতি গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে বাধ্য করবে।
একইভাবে, দেশের মূলধারার গণমাধ্যমগুলো জলবায়ু সংকটের কারণে দেশের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ক্ষতি, স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও বাস্তুচ্যুত মানুষের দুর্ভোগের ওপর নিয়মিত বিশেষ প্রতিবেদন, টক-শো প্রচার এবং জনমত জরিপ পরিচালনা করতে পারে। এতে দেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বিষয়টির অগ্রাধিকার পাওয়ার সম্ভাবনা ত্বরান্বিত হবে। ফলে সরকার জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর ভর্তুকি হ্রাস, নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কার্বন নিঃসরণ নির্ধারিত মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ ও সবুজ প্রযুক্তির বিকাশ এবং বাস্তবায়নে আরও বেশি তৎপর হবে।
এমতাবস্থায় প্রত্যাশার বিষয় হলো- বন ও পরিবেশ বিষয়ক বেশকিছু আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্যোগে ইতোমধ্যে সরকারি-বেসরকারি সংস্থা এবং বহু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় দেশের নানা স্থানে তরুণ সমাজ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও জলবায়ুগতভাবে বিপর্যস্ত এলাকার বাসিন্দাদের জন্য নিয়মিত সভা, সেমিনার, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ আয়োজনের পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকারের সহাযোগিতায় এই পদক্ষেপগুলোকে সর্বাত্মকভাবে কার্যকর করা গেলে নিঃসন্দেহে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক সংকট নিরসনে বাংলাদেশ আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে।
লেখক : কবি, সাংবাদিক, কলামিস্ট ও ব্লগার।
খুলনা গেজেট/এনএম