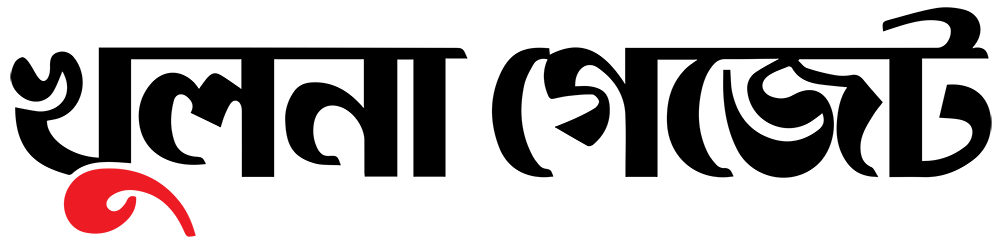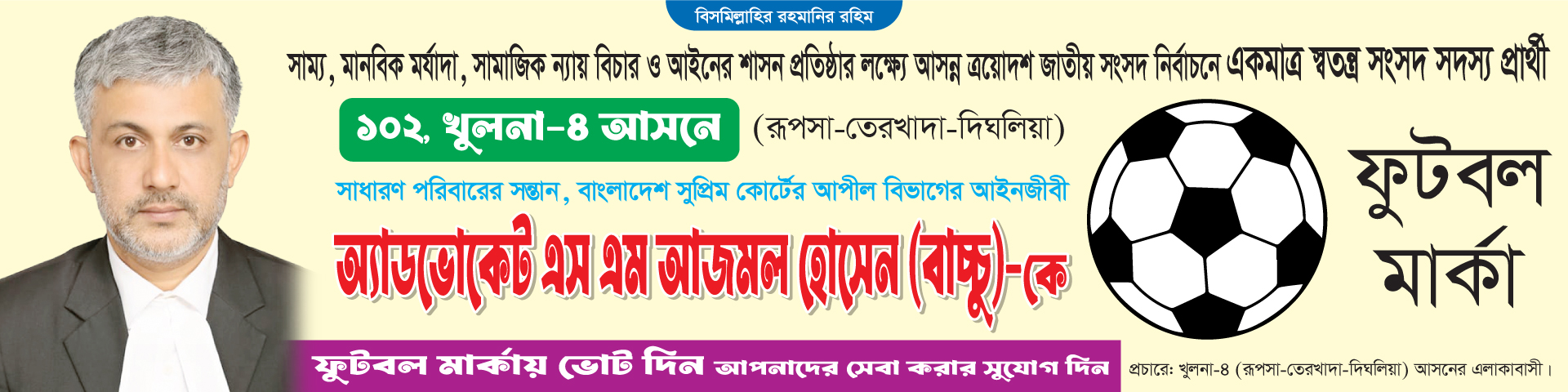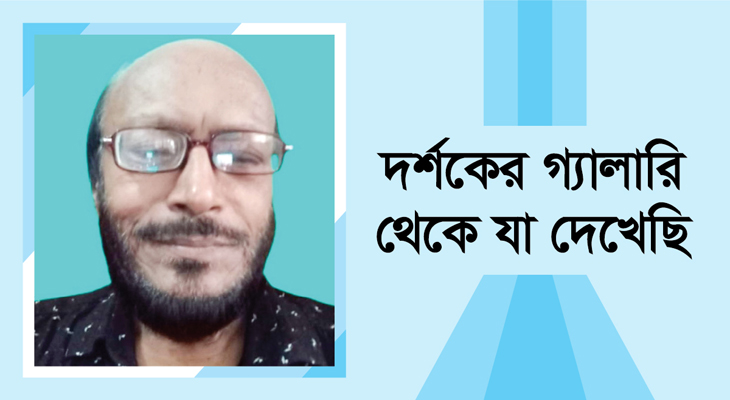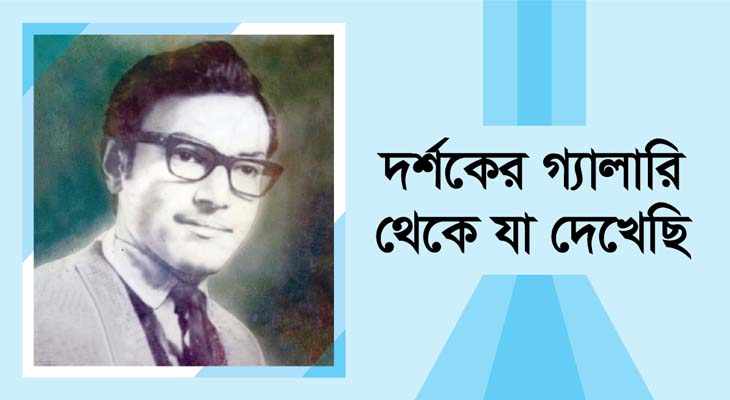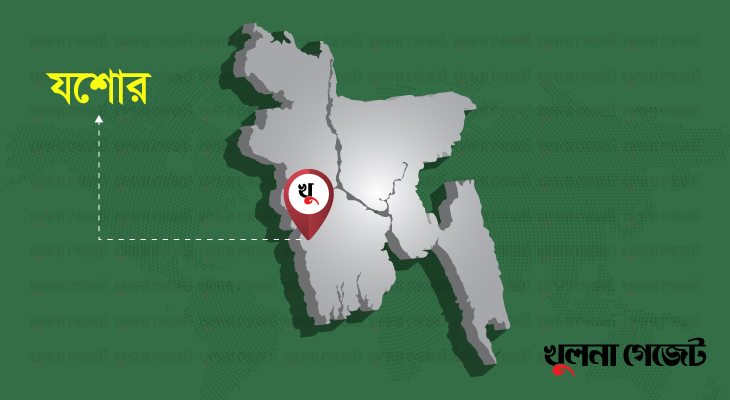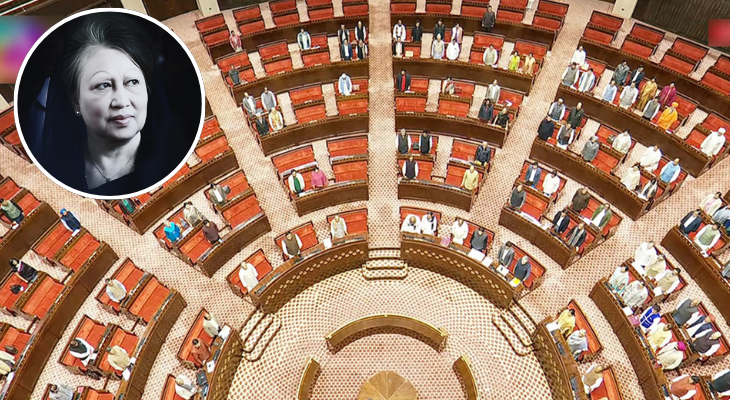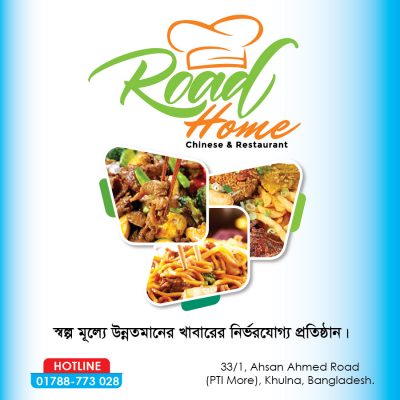বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল; মানচিত্রে এটি একটি ভূখ- মাত্র কিন্তু বাস্তবে এটি এক প্রাত্যহিক রণাঙ্গন। এই রণাঙ্গনের একপাশে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াল রূপ সমুদ্রের ক্রমবর্ধমান উচ্চতা, মাটির লবণাক্ততা, প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় আর তীব্র নদী ভাঙন। অন্যপাশে দাঁড়িয়ে আছে এই জনপদের লক্ষ লক্ষ নিঃস্ব মানুষ। এটি কোনো গতানুগতিক জীবনযাপন নয়। এটি একটি অঘোষিত জলবায়ু যুদ্ধ। আর এই যুদ্ধের সম্মুখসারির যোদ্ধারা হলেন আমাদের উপকূলের সেই অদম্য মানুষগুলো, যারা কোনো অপরাধ না করেও জলবায়ু পরিবর্তনের নির্মম শিকার।
প্রতিদিন সকালে ঘুম ভেঙে এই মানুষগুলোকে বেঁচে থাকার নতুন লড়াই শুরু করতে হয়। তাদের লড়াই সুপেয় পানির জন্য, তাদের লড়াই এক চিলতে ফসলি জমির জন্য, তাদের লড়াই ভিটেমাটি আঁকড়ে ধরে রাখার জন্য। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম বা বড় বড় সেমিনারে যখন ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যাডাপটেশন নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা হয়, তখন এই মানুষগুলো সেই তত্ত্বকে বাস্তবে রূপ দেন নিজেদের রক্ত, ঘাম এবং শেষ সম্বলটুকু দিয়ে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বা আন্তর্জাতিক অর্থায়ন ছাড়াই সম্পূর্ণ খালি হাতে তারা এই অসম লড়াই আর কতদিন চালিয়ে যাবেন?
উপকূলের এই যোদ্ধারা লড়ছেন সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে। যখন সমুদ্রের আগ্রাসী নোনাজল তাদের ফসলের মাঠ আর পুকুরের মিঠা পানিকে বিষাক্ত করে তুলছে, তখন তারা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। যে কৃষক প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সোনালি ধান চাষ করতেন, তিনি আজ বাধ্য হয়ে লবণ-সহিষ্ণু জাতের ফসল আবাদের চেষ্টা করছেন, যা প্রায়শই অলাভজনক। অনেকে ধানের বদলে চিংড়ি চাষ শুরু করেছিলেন, কিন্তু সেই চিংড়ি ঘেরও ঘন ঘন দুর্যোগে ভেসে যাচ্ছে।
যখন জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা বাড়ছে, তখন তারা ধারদেনা করে বা শেষ সম্বলটুকু বিক্রি করে ঘরের ভিটে এক ফুট উঁচু করছেন। এই ভিটে উঁচু করার প্রক্রিয়াটি কোনো সরকারি প্রকল্প নয়, এটি তাদের ব্যক্তিগত লড়াই। যে কৃষক একসময় জমিতে লাঙল চালাতেন, লবণাক্ততা তার জমি কেড়ে নেওয়ায় সে আজ পেশা পরিবর্তন করে নদীতে মাছ ধরছেন বা দিনমজুরে পরিণত হচ্ছেন।
এই খাপ খাইয়ে নেওয়া বা অভিযোজন প্রক্রিয়াটি কোনো তাত্ত্বিক শব্দ নয়। এর প্রতিটি ধাপেই রয়েছে বিপুল আর্থিক বিনিয়োগ। একটি লবণ-সহিষ্ণু ফসলের বীজ কেনা, একটি পুকুরকে লবণাক্ততা থেকে রক্ষা করা, ঝড়ের পর ঘর মেরামত করা বা পেশা পরিবর্তন করে নতুন জীবিকা খোঁজা এর প্রতিটির জন্যই অর্থের প্রয়োজন। এই ব্যয়বহুল লড়াই তারা চালিয়ে যাচ্ছে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে। এই অসম লড়াইয়ে তাদের ব্যক্তিগত সামর্থ্য যে ফুরিয়ে আসছে, তা বোঝার জন্য বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই।
একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তা অনস্বীকার্য। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের মতো একটি অস্তিত্বের সংকট মোকাবিলায় আমাদের জাতীয় অগ্রাধিকার কী, তা প্রতিফলিত হয় আমাদের জাতীয় বাজেটে। উপকূলীয় সুরক্ষা এবং অভিযোজনের জন্য প্রতি বছর যে বরাদ্দ রাখা হয়, তা কি প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট?
বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF) গঠিত হয়েছে, যা নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু মোকাবিলার একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কিন্তু, এই তহবিলের আকার এবং উপকূলীয় অঞ্চলের বিশাল চাহিদা বিবেচনা করলে এই বরাদ্দকে অপ্রতুলই বলতে হয়। তদুপরি, যেটুকু বরাদ্দ আসে, তা প্রায়শই ব্যয় হয় তাৎক্ষণিক বা জরুরি মেরামতের কাজে। টেকসই, দীর্ঘমেয়াদী এবং জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণে যে ধরনের বড় বিনিয়োগ প্রয়োজন, তার অভাব সুস্পষ্ট।
যখন একটি বেড়িবাঁধ ভেঙে যায়, তখন তা জরুরি মেরামত করা হয়। সেই দুর্বল বাঁধ পরের জলোচ্ছ্বাসেই আবার ভেঙে যায়। এই চক্রাকার ব্যর্থতার পেছনে রয়েছে বরাদ্দের স্বল্পতা এবং সেই বরাদ্দের ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব। উপকূলীয় সুরক্ষার জন্য একটি সমন্বিত, দীর্ঘমেয়াদী ও বৃহৎ বিনিয়োগ পরিকল্পনা ছাড়া কেবল খ-িত প্রকল্প দিয়ে এই বিপর্যয় ঠেকানো সম্ভব নয়।
এই সংকটের মূল প্রোথিত রয়েছে জলবায়ু অবিচাচারের ধারণার মধ্যে। যে উন্নত দেশগুলোর লাগামহীন কার্বন নিঃসরণ এবং শিল্পায়নের ফলে আজ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ঘটছে, সেই দেশগুলো এই বিপর্যয়ের জন্য ঐতিহাসিকভাবে দায়ী। অথচ এর সবচেয়ে নির্মম শিকার হচ্ছে বাংলাদেশের মতো দেশগুলো, যাদের কার্বন নিঃসরণের দায় ইতিহাসে প্রায় শূন্য।
এই ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা থেকেই উন্নত দেশগুলো প্রতি বছর উন্নয়নশীল দেশগুলোকে জলবায়ু অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। প্যারিস চুক্তি থেকে শুরু করে প্রতি বছরের জলবায়ু সম্মেলনে (COP) এই নিয়ে অনেক কথা হয়। লস অ্যান্ড ড্যামেজ বা ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় একটি বিশেষ তহবিল গঠনের ঘোষণাও এসেছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সেই প্রতিশ্রুত অর্থায়ন আজও একটি মরীচিকা হয়েই আছে।
যে সামান্য অর্থায়ন পাওয়া যায়, তা আসে ঋণ হিসেবে, অনুদান হিসেবে নয়। অথবা তা এমন সব জটিল শর্তের জালে আটকা পড়ে থাকে যে, প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে তা পৌঁছাতেই পারে না। এই অর্থায়ন প্রাপ্তিতে আমাদের কূটনৈতিক ব্যর্থতা যেমন রয়েছে, তার চেয়েও বেশি রয়েছে উন্নত বিশ্বের রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব। তারা জলবায়ু পরিবর্তনকে একটি মানবিক সংকট হিসেবে না দেখে, এটিকে একটি দর-কষাকষির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। এটিই জলবায়ু অবিচারের সবচেয়ে নগ্ন এবং নিষ্ঠুরতম রূপ।
অর্থায়ন ছাড়া উপকূলের এই একতরফা লড়াইয়ের ভবিষ্যৎ কী? এর পরিণতি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং এরই মধ্যে তা দেশব্যাপী দৃশ্যমান। সেই পরিণতি হলো ব্যাপকহারে জলবায়ু অভিবাসন।
যখন একজন কৃষক তার জমি হারান, যখন একজন জেলে তার জীবিকা হারান, যখন একজন মানুষ বারবার দুর্যোগে সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েন, তখন তার সামনে একটিই পথ খোলা থাকে ভিটেমাটি ত্যাগ করা। এই মানুষগুলোই জলবায়ু শরণার্থীতে পরিণত হচ্ছেন। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ উপকূলীয় অঞ্চল ছেড়ে পাড়ি জমাচ্ছেন শহরের বস্তিগুলোতে।
ঢাকা, চট্টগ্রাম বা খুলনার মতো বড় শহরগুলোর ওপর এই জলবায়ু শরণার্থীদের চাপ প্রতিনিয়ত বাড়ছে। এর ফলে কেবল শহরের নাগরিক সেবাই ভেঙে পড়ছে না, তৈরি হচ্ছে তীব্র সামাজিক অস্থিতিশীলতা, বাড়ছে অপরাধ এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য। উপকূলের এই নীরব বিপর্যয় আজ আর কেবল দক্ষিণাঞ্চলের আঞ্চলিক সমস্যা নয়। এটি আজ সমগ্র বাংলাদেশের জন্য একটি জাতীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্থায়িত্বের সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে।
তাই আজ স্পষ্ট করে বলার সময় এসেছে, উপকূলের জন্য জলবায়ু অর্থায়ন কোনো সহানুভূতি বা সাহায্য নয়। এটি তাদের অধিকার। এটি উন্নত বিশ্বের ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা, যা তাদের অবশ্যই পূরণ করতে হবে। এই অর্থায়ন আদায়ের জন্য আমাদের কূটনৈতিক তৎপরতাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিতে হবে। একইসাথে, আমাদের জাতীয় বাজেটেও উপকূলকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং সেই অর্থের স্বচ্ছ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
কারণ, এই অর্থায়ন ছাড়া উপকূলের মানুষগুলোর এই অদম্য, একতরফা লড়াই একসময় থেমে যাবে। টিকে থাকার শেষ চেষ্টাও যখন ব্যর্থ হবে, তখন তারা রণে ভঙ্গ দেবে। আর সেই লড়াই থেমে গেলে তার পরিণতি একা উপকূলবাসী নয়, পুরো বাংলাদেশকেই ভোগ করতে হবে। উপকূলকে অরক্ষিত রেখে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখা অসম্ভব।
লেখক : পরিবেশবাদী লেখক, সংগঠক ও কলামিস্ট।
খুলনা গেজেট/এনএম