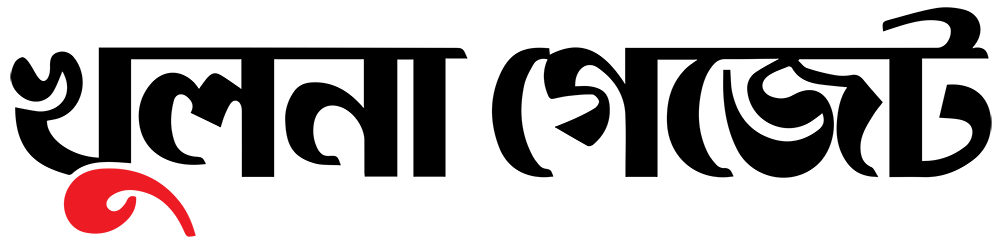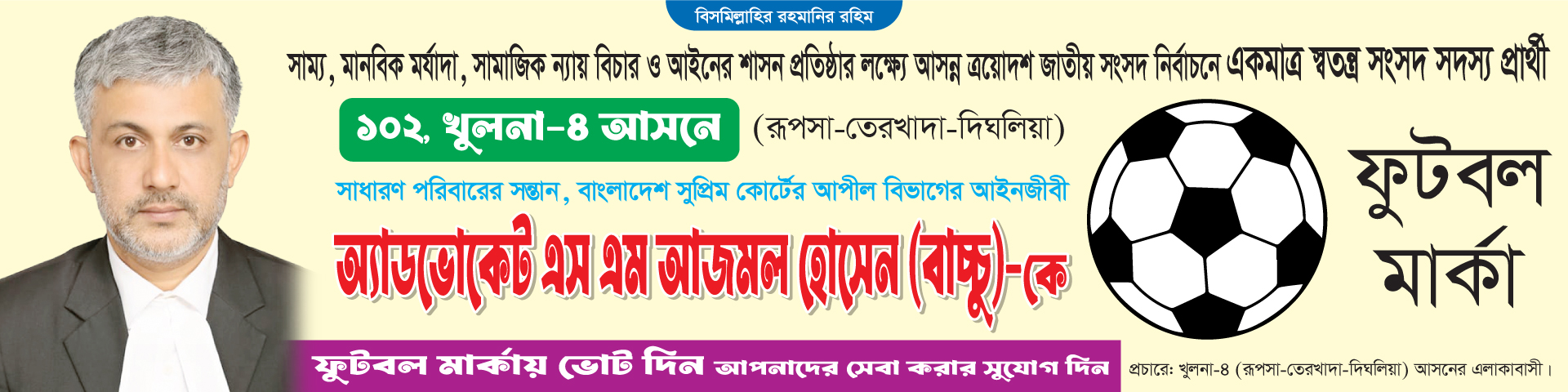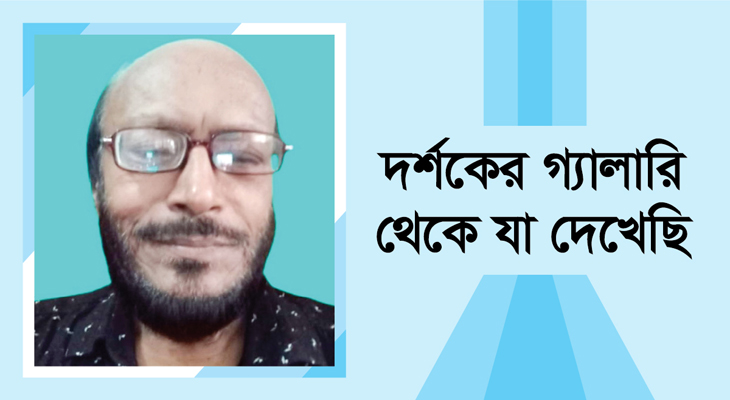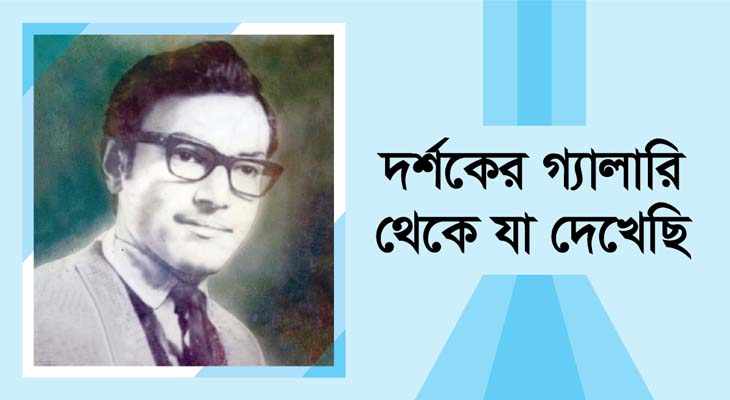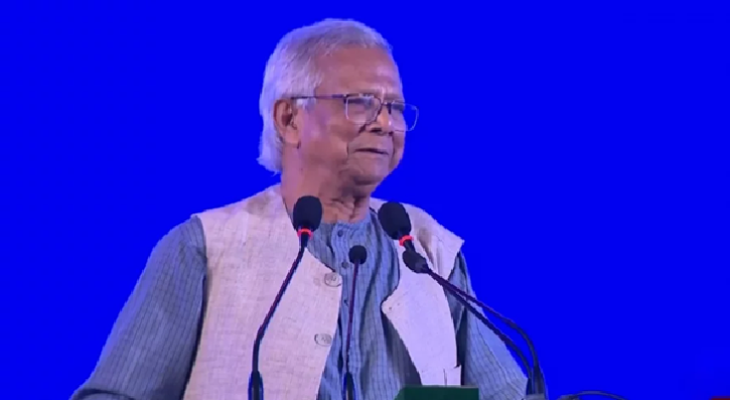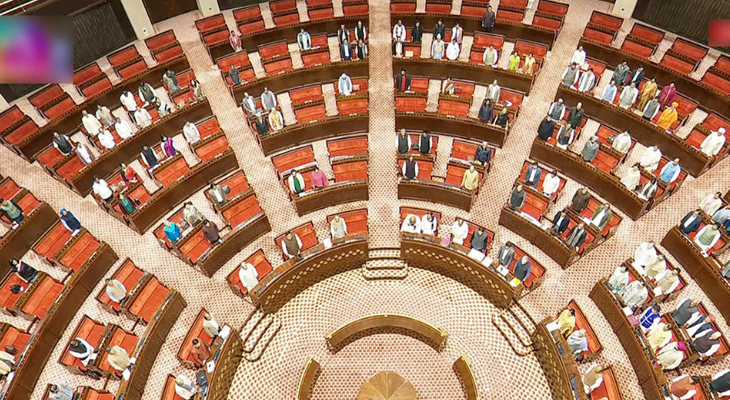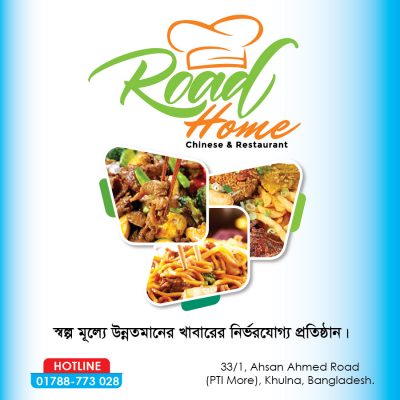বাংলাদেশের নির্বাচনী সংস্কৃতিতে একটি দীর্ঘদিনের অদ্ভুত বাস্তবতা আছে প্রার্থী হতে হলে শুধু রাজনৈতিক পরিচয় বা জনসমর্থনই যথেষ্ট নয়; এর সঙ্গে যুক্ত থাকে প্রচুর অর্থব্যয়, নিজ উদ্যোগে প্রচারসামগ্রী তৈরি এবং শেষে সেটিকে ‘প্রচারে এলাকাবাসী’ বলে চালিয়ে দেওয়ার চল। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত অনেকে এই চর্চাকে শুধু বিব্রতকর নয়, বরং জনগণের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্কের মধ্যে একটি কৃত্রিম ব্যবধান তৈরি করার অন্যতম কারণ হিসেবে দেখেন।
সম্প্রতি জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম মুখ্য সংগঠক ডাঃ মাহমুদা মিতুর একটি ফেসবুক পোস্ট এই বাস্তবতাকে নতুন করে আলোচনায় এনেছে। অনুসারীদের বানানো একটি ফটোকার্ড শেয়ার করে তিনি লিখেছেন নির্বাচনে অংশ নিতে হলে নিজের অর্থে পোস্টার ছাপিয়ে, নিজেই প্রচার চালাতে হয়; অথচ তার নিচে ‘প্রচারে এলাকাবাসী’ লেখা দেওয়া হয়। তাঁর ভাষায়, ভাবলেই ‘শরম’ লাগে।
ডাঃ মিতুর বক্তব্য রাজনীতির একটি নীরব সত্যকে উন্মোচন করে প্রচার অর্থায়নে জনগণ নয়, বরং প্রার্থীই হন প্রধান ব্যয়কারী; তবুও সেটি জনগণের পক্ষ থেকে এসেছে বলে উপস্থাপন করা হয়। যেন জনগণ আগ্রহী, সক্রিয় এবং উদগ্রীব; অথচ বাস্তবতায় অনেক সময় জনগণ কেবল দেখেন, একটি ‘বাধ্যতামূলক উদ্দীপনা’র রাজনীতি কীভাবে শেকড় গেড়ে বসল।
ইউনিয়ন পরিষদ থেকে শুরু করে সংসদ নির্বাচন সবক্ষেত্রেই একই চিত্র। প্রার্থীরা জানেন, জনপ্রিয়তা প্রমাণের প্রথম ধাপ শক্তিশালী প্রচারণা; আর সেই প্রচারণার ভিত্তি হলো অর্থনৈতিক সক্ষমতা। নেতৃত্বের যোগ্যতা, সংগঠন পরিচালনার অভিজ্ঞতা কিংবা নৈতিক অবস্থান এসবের আগে আসে
প্রশ্ন : প্রার্থী কি অর্থ ব্যয় করতে সক্ষম? দলীয় মনোনয়ন প্রক্রিয়াতেও এই বিবেচনা আজ প্রকাশ্য গোপন সত্য।
এ অবস্থাকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম রাষ্ট্রচিন্তক অমর্ত্য সেন এর গণতন্ত্র তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। তিনি বলেছেন “গণতন্ত্র শুধু ভোটের ব্যবস্থা নয়; গণতন্ত্র হলো জনসম্পৃক্ততার প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা।”
(Development as Freedom, 1999)
অর্থাৎ, যখন জনগণ কেবল নির্বাচনের দর্শক হয়ে যায় এবং প্রার্থী প্রচারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে ‘এলাকাবাসী’ নামের আবরণ ব্যবহার করেন, তখন প্রকৃত গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ ক্ষীণ হয়ে পড়ে। গণতন্ত্র তখন একটি আনুষ্ঠানিকতা; অংশগ্রহণ তখন ভৌতিক।
‘প্রচারে এলাকাবাসী’ শব্দ দুটো দীর্ঘদিন ধরে জনপ্রতিনিধিত্বের প্রারম্ভিক পরিচয়ের জায়গায় ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো : জনগণের নামে প্রচারণা চালানো আর জনগণকে রাজনীতির অংশীদার করে তোলা এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?
পার্থক্য হলো এজেন্সিতে কোনো কাজ মানুষ নিজের সিদ্ধান্তে করছে, নাকি তাকে দিয়ে করানো হচ্ছে।
বাস্তব চিত্র হলো- ক) প্রচার হয় প্রার্থীর অর্থে খ) সংগঠন হয় অনুগত গোষ্ঠীর মাধ্যমে গ) আর জনসম্পৃক্ততা দেখানো হয় কৃত্রিমভাবে ফলাফল গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভিত ক্ষয়ে যায়, রাজনীতির ওপর আস্থা দুর্বল হয়, আর নেতৃত্ব নির্বাচন প্রক্রিয়া ক্রমে অর্থের প্রতিযোগিতায় রূপান্তরিত হয়।
সমাধান একদিনে আসার মতো সহজ নয়। তবে প্রথম পদক্ষেপগুলো স্পষ্ট :
১) নির্বাচনী ব্যয়ের স্বচ্ছতা বাস্তবায়ন সংখ্যাটি আইনপত্রে নয়, মাঠে কার্যকর হতে হবে
২) দলের ভেতরে নেতৃত্ব গঠনের কাঠামো শক্তিশালী করা ক্ষমতার দরজা অর্থে নয়, কাজে খুলতে হবে
৩) জনসম্পৃক্ততার বাস্তব সুযোগ সৃষ্টি করা জনগণ যেন দর্শক নয়, অংশীদার হন
ডাঃ মিতুর মন্তব্য তাই কেবল ব্যক্তিগত অস্বস্তির প্রকাশ নয়; এটি একটি রাজনৈতিক ধারাবাহিকতার সংকেত। যদি রাজনীতি সত্যিই জনগণের হয়, তাহলে জনগণকে আর প্রতীকী প্রপস হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না; বরং তাঁরা সত্যিকারের অংশীদার হবেন। গণতন্ত্র টেকে আস্থায়। আর আস্থা টিকে সত্যিকার অংশগ্রহণে। এখন প্রশ্ন আমরা কি সেই গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করতে প্রস্তুত?
লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক ও কলামিস্ট
email: niazjournalist@gmail.com
খুলনা গেজেট/এনএম