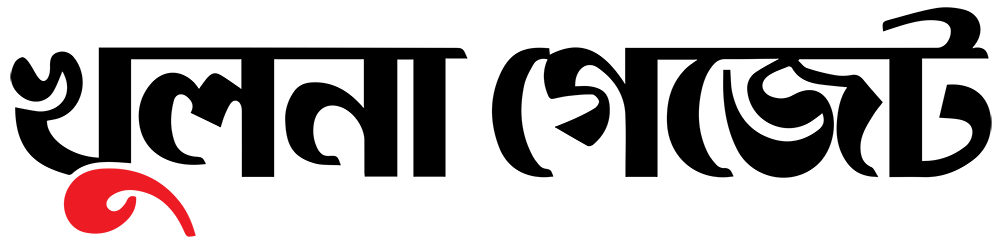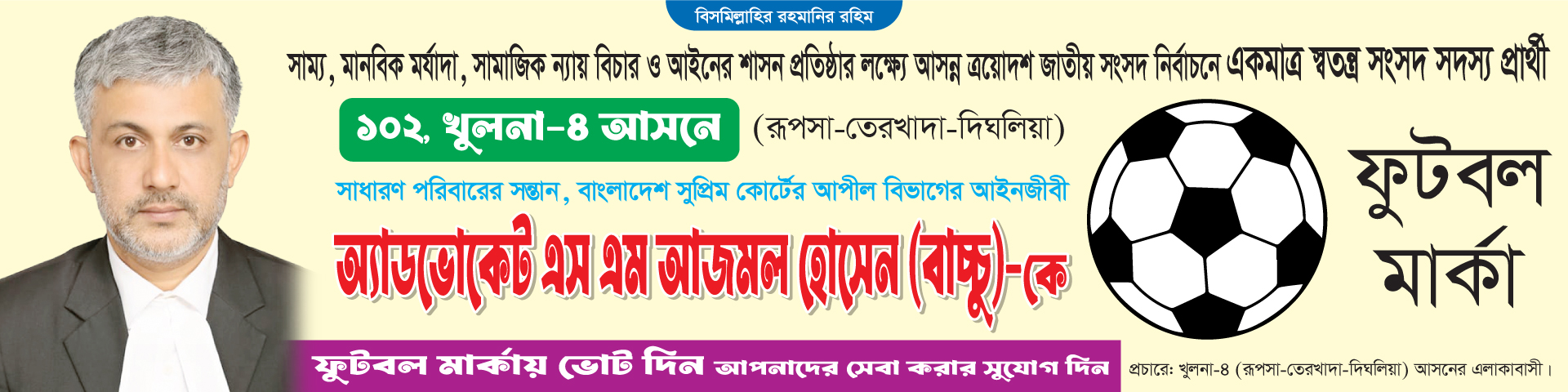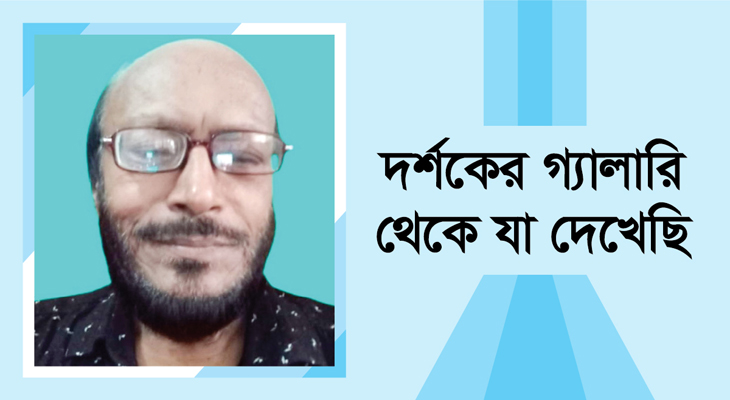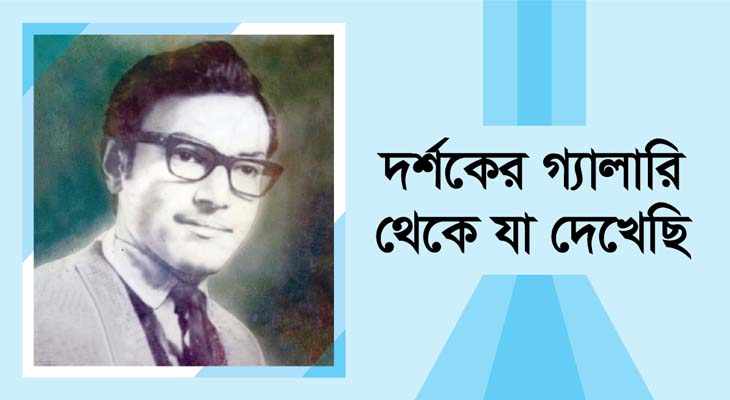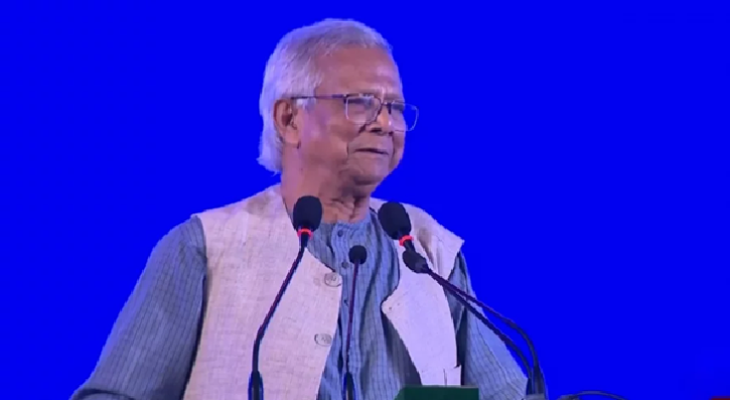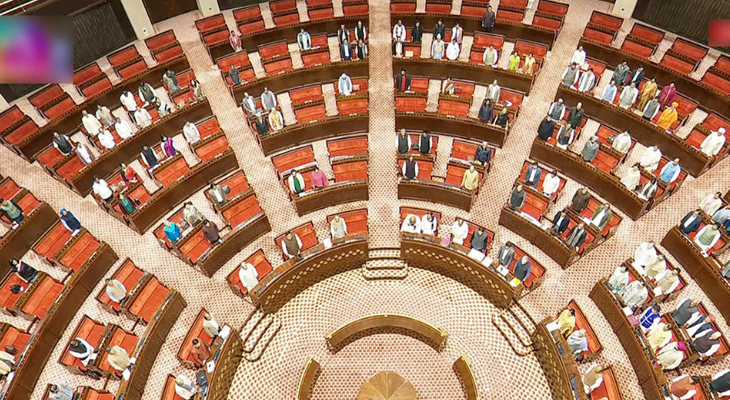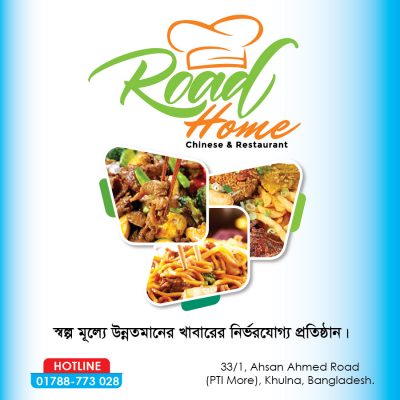আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ‘দ্বিচারিতা’ নতুন কিছু নয়। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ যখন একই সপ্তাহে দুটি পরস্পরবিরোধী কূটনৈতিক বক্তব্য প্রকাশ করেন তখন তা কেবল একটি দেশের নীতি নয়, বরং বৈশ্বিক ক্ষমতার সামঞ্জস্য নিয়ে প্রশ্ন তোলে।
গত ৩১ অক্টোবর বাহরাইনে অনুষ্ঠিত বার্ষিক নিরাপত্তা সম্মেলন ‘মানামা সংলাপ’-এ যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালক তুলসী গ্যাবার্ড ঘোষণা দেন- ট্রাম্প প্রশাসন আর অন্য কোনো দেশের সরকার বদলের নীতি অনুসরণ করছে না। অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্র এখন অন্য দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ না করে স্বনির্ভর গণতন্ত্রকে সম্মান জানাবে।
কিন্তু তার কয়েক দিন পর ২ নভেম্বর মার্কিন টেলিভিশন চ্যানেল সিবিএস নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, “ভেনেজুয়েলার নিকোলাস মাদুরোর ক্ষমতায় থাকার সময় শেষ!” এই দুটি বক্তব্য একসঙ্গে মিলিয়ে দেখলে যে অসঙ্গতি, সেটিই আধুনিক মার্কিন কূটনীতির মৌলিক সংকট।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে আমেরিকা নিজেকে মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার অভিভাবক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু বাস্তবে এই নীতির আড়ালে বহির্বিশ্ব বিশেষত মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকায় বারবার চালানো হয়েছে ‘রেজিম চেঞ্জ’ বা সরকার বদলের গোপন ও প্রকাশ্য তৎপরতা।
১৯৫৩ সালে ইরানে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত মোহাম্মদ মোসাদ্দেককে ক্ষমতাচ্যুত করা, ১৯৭৩ সালে চিলিতে সামরিক অভ্যুত্থানে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সালভাদর আলেন্দেকে উৎখাত, ২০০১ সালে আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালানো, ২০০৩ সালে “মাস ডেসট্রাক্টিভ উইপন্স” সংরক্ষণের মিথ্যা অভিযোগে ইরাক আক্রমণ এবং ২০১১ সালে উত্তর আফ্রিকার দেশ লিবিয়ায় গৃহযুদ্ধ উসকে দিয়ে গাদ্দাফির পতন ঘটানোর মতো দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে আমেরিকার এই “গণতন্ত্র রপ্তানি”- এর ইঞ্জেকশন আসলে একপ্রকার ভূরাজনৈতিক প্রকল্প।
কারণ, উপরোক্ত দেশগুলোর মতো যখনই ভূরাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কোনো রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী কোনো সরকার ক্ষমতায় এসেছে, তখনই তাদেরকে ‘অগণতান্ত্রিক’, ‘মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী’ বা ‘দুর্নীতিগ্রস্ত’ আখ্যা দিয়ে রাজনৈতিক চাপ, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, এবং শেষে সামরিক হস্তক্ষেপের পথ বেছে নেওয়া হয়েছে।
ট্রাম্প আমলে সেই নীতির পুনর্মূল্যায়নের দাবি উঠেছিল। ট্রাম্পও নিজেকে ‘অ্যান্টি-ওয়ার’ প্রেসিডেন্ট হিসেবে উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হওয়ার পর। এমনকি ইসরায়েল-ফিলিস্তিন যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবনা উত্থাপনের সময় শান্তিতে নোবেলও চেয়ে বসেছিলেন তিনি। তারই ধারাবাহিকতায় গত ৩১ অক্টোবর দেশটির হাওয়াই অঙ্গরাজ্য থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস সদস্য, মার্কিন জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালক এবং এবং ইরাক যুদ্ধের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সেনা তুলসী গ্যাবার্ড এক বিবৃতিতে বলেছিলেন “আমরা আর অন্য দেশের সরকারের ওপর আমাদের ইচ্ছা চাপিয়ে দেব না।”
কথাটি যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘ কূটনৈতিক ইতিহাসে একপ্রকার নৈতিক আত্মসমালোচনার মতো শোনালেও সেই আত্মসমালোচনার কিছু দিন পার না হতেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় বিপরীত সুর। তিনি নিজ দেশের ফেন্টানিল মাদক বিস্তারের দায় চাপিয়ে দেন ভেনেজুয়েলার ওপর। শুধু তাই নয়, তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন : “মাদুরোর সময় ফুরিয়ে এসেছে!”
এ দিকে, তাঁর পরোক্ষ নির্দেশে ইতোমধ্যে বেশকিছু মার্কিন রণতরী ক্যারিবীয় সাগর ও ভেনেজুয়েলীয় উপকূলের কাছে মোতায়েন রয়েছে। এলাকাটিতে বেশ কয়েকটি ছোট জলযানকে ‘ফেন্টানিলবাহী মাদক চোরাকারবারি’ আখ্যা দিয়ে হামলা চালিয়ে অন্তত ৬১ জনকে হত্যা করা হয়েছে বলেও খবর এসেছে কিছু গণমাধ্যমে। যা ট্রাম্প ও তুলসীর বক্তব্যকে পরস্পরবিরোধী করে তুলেছে।
দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন হস্তক্ষেপ বিরোধী একটি রাষ্ট্র হিসেবে ভেনেজুয়েলা পরিচিত। দেশটির প্রেসিডেন্ট হুগো শাভেজ কিংবা নিকোলাস মাদুরো উভয় নেতাই সমাজতান্ত্রিক নীতি ও লাতিন আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী বলয় গঠনের চেষ্টা করেছেন। তাই ওয়াশিংটনের চোখে তারা ‘শত্রু’। ট্রাম্প যখন বলেন, “মাদুরোর সময় শেষ” তখন আসলে তিনি সেই পুরোনো ‘মনরো ডকট্রিন’-এর পুনরাবৃত্তি করেন যে নীতি মোতাবেক আমেরিকা লাতিন অঞ্চলে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকে বৈধ মনে করে।
অন্য দিকে, গ্যাবার্ডের বক্তব্যে একধরনের ‘কূটনৈতিক আত্মসংযম’- এর ইঙ্গিত থাকলেও আমেরিকার অভ্যন্তরীণ জটিল ক্ষমতা কাঠামোর কারণে তা বাস্তব সিদ্ধান্ত হিসেবে ভিন্ন পথে চলে গেছে। মূলত ‘ডিপ স্টেট’, অর্থাৎ সামরিক-বাণিজ্যিক জোট ও গোয়েন্দা সংস্থার মতো অদৃশ্য প্রভাবগোষ্ঠী বহুদিন ধরেই মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির নিয়ন্ত্রক হিসেবে বিদ্যমান। এ কারণেই গ্যাবার্ডের মানবিক কৌশলগত কূটনীতির বয়ান ও ট্রাম্পের আগ্রাসী ঘোষণা একই প্রশাসনের ভেতর সহাবস্থান করতে পারে।
আবার, এই দ্বিচারিতার কারণ অভ্যন্তরীণ নীতির পাশাপাশি একটি মার্কিন কূটনীতির কৌশলগত চালও বটে। এক দিকে যুক্তরাষ্ট্র ‘মানবাধিকার রক্ষার’ মুখোশ পরে নৈতিক উচ্চতা ধরে রাখতে চাইলেও, আদতে বিশ্বব্যাপী নিজের অর্থনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করাই দেশটির আবহমানকালের প্রকৃত লক্ষ্য। ফলে এক মুখে তারা বলে ‘আমরা হস্তক্ষেপ করি না’, আর অন্য মুখে চাপিয়ে দেয় নিষেধাজ্ঞা, অর্থনৈতিক অবরোধ কিংবা ‘নো-ফ্লাই জোন’-র মতো কড়াকড়ি।
এই কৌশলকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা চিহ্নিত করেন “স্ট্র্যাটেজিক অ্যাম্বিগুইটি” অর্থাৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অস্পষ্টতা হিসেবে। এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র এক দিকে কূটনৈতিক নমনীয়তা বজায় রাখে, অন্য দিকে যেকোনো মুহূর্তে শক্তি প্রয়োগের বৈধতা তৈরির সুযোগ লুফে নেয়। ভেনেজুয়েলার ক্ষেত্রে ঠিক এমনটিই ঘটছে। তারা নিছক ‘মাদকবিরোধী সংগ্রাম’ আর ‘গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের’ কথা বলে মাদুরোর সরকারের পতনের আহ্বান জানিয়ে যেন স্ব-ঘোষিত মোড়লের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছে।
এই দ্বিমুখী নীতির স্বরূপ সবচেয়ে বড় সংকট তৈরি করছে আন্তর্জাতিক আস্থার ক্ষেত্রে। লাতিন আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য কিংবা দক্ষিণ এশিয়া সব অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর আস্থার সংকট বাড়ছে। দেশগুলো বুঝতে পারছে, ওয়াশিংটনের ‘গণতন্ত্র’ মূলত একটি রপ্তানি পণ্য, যার গন্তব্য নির্ধারিত হয় তেল, গ্যাস বা ভূ-রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের মাপকাঠিতে। ফলে চীন ও রাশিয়ার মতো রাষ্ট্র ক্রমেই বিকল্প শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে।
এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব নাগরিকরাও এখন প্রশ্ন তুলছেন, এই অবিরাম হস্তক্ষেপনীতি আদৌ যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা বাড়াচ্ছে নাকি সংকটকে ঘনীভূত করছে? আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার, ইরাক যুদ্ধে বিলিয়ন বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতি, কিংবা লিবিয়ায় গৃহযুদ্ধের স্থায়িত্বই প্রমাণ করে, একদেশের রাজনৈতিক নকশা অন্য দেশে আরোপের চেষ্টা শেষমেষ বুমেরাং হয়ে ওঠে।
এতদাসত্ত্বেও, তুলসী গ্যাবার্ডের বক্তব্যে যে কৌশলগত মানবিকতার আহ্বান ছিল, তা নিঃসন্দেহে এক ধরনের আদর্শিক প্রতিবাদ। কিন্তু বাস্তবে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি কেবল ব্যক্তিগত অবস্থান দিয়ে বদলায় না। গ্যাবার্ড হয়তো বুঝেছিলেন ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক অবিশ্বাসের যুগে ‘নন-ইন্টারভেনশনিস্ট’ নীতি গ্রহণ যুক্তরাষ্ট্রের জন্য টেকসই পথ। কিংবা কূটনৈতিক চাল হিসেবে সেভাবেই সমগ্র বিষয়টিকে উপস্থাপন করেছিলেন তিনি।
কিন্তু তাঁর সেই আহ্বান ট্রাম্পের রাজনৈতিক রণকৌশলে গুরুত্ব পায়নি। বরং ট্রাম্পের বক্তব্য স্পষ্ট করে দেয়, ওয়াশিংটন এখনো ভূ-রাজনৈতিভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে নিজেদের স্বার্থরক্ষার খাতিরে ‘রেজিম চেঞ্জ’- এর প্রলোভন ছাড়তে পারেনি।
অথচ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস বলে, নৈতিকতা যতবার কূটনীতির অঙ্গনে জায়গা হারিয়েছে, ততবারই যুদ্ধ ও সংকট প্রকট হয়ে উঠেছে। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি সত্যিই বিশ্বে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের মূল্যবোধ ছড়াতে চায়, তবে প্রথমে নিজেদের নীতি-প্রণয়নে সততা আনতে হবে। “আমরা হস্তক্ষেপ করব না” বলার কয়েক দিনের মাথায় অন্য দেশের সরকারের পতন চাওয়ার অর্থ কেবল কপটতা নয়, বরং এক ধরনের নৈতিক দেউলিয়াপনা।
যে যা-ই বলুক না কেন, বিশ্ব এখন ধীরে ধীরে বহুমেরু বাস্তবতার দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। শেষ হচ্ছে একক আধিপত্যের যুগ। এই প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের উচিত হবে নীতিগত ধারাবাহিকতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা পুনর্গঠন করা। এর মধ্য দিয়ে গ্যাবার্ডের ইতিবাচক ঘোষণার মতো বক্তব্য শুধুই প্রতীকী নয়, বরং বাস্তব নীতিতে প্রতিফলিত হবে। অন্যথায় ট্রাম্পের মতো নেতাদের মুখে উচ্চারিত “আমেরিকা ফার্স্ট” স্লোগান আসলে অন্য সবার ক্ষতির সমার্থক হয়ে উঠবে।
মার্কিন কূটনীতির ভবিষ্যৎ তাই নির্ভর করছে এক প্রশ্নের ওপর তারা কি সত্যিই বিশ্বকে সমান অংশীদার হিসেবে দেখবে, নাকি আগের মতোই ক্ষমতার ছায়াতলে নতুন বিশ্বব্যবস্থা নির্মাণের পুরোনো খেলায় মেতে থাকবে?
লেখক : শিক্ষার্থী, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।
খুলনা গেজেট/এনএম